আজকের বিশ্বে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া বৈশ্বিক আর্থিক সংকট এবং ইউরোর চলমান সংকট – উভয়ই গত তিন দশকে উদ্ভূত স্বল্প নিয়ন্ত্রিত আর্থিক পুঁজিবাদের মডেলের ফলাফল। তবুও, ওয়াল স্ট্রিটের বেইলআউট নিয়ে জনসাধারণের প্রচণ্ড ক্ষোভ সত্ত্বেও, আমেরিকায় বামপন্থী গণআন্দোলনের কোনো বড় উত্থান ঘটেনি। Occupy Wall Street আন্দোলনটি কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলির সবচেয়ে সক্রিয় ও গতিশীল জনআন্দোলন হয়েছে ডানপন্থী “টি পার্টি”, যার প্রধান লক্ষ্য সেই নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র—যে রাষ্ট্র সাধারণ মানুষকে আর্থিক জল্পনাবিদদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।
ইউরোপেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে—বামপন্থীরা নিস্তেজ, অথচ ডানপন্থী জনতাবাদী দলগুলো ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।
বামপন্থী আন্দোলনের এই দুর্বলতার পিছনে অনেক কারণ থাকলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো ধারণার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। গত প্রজন্মজুড়ে অর্থনৈতিক বিষয়ে মতাদর্শিক নেতৃত্ব দখল করে রেখেছে লিবারটেরিয়ান বা চরম স্বাধীনতাবাদী ডানপন্থা। অন্যদিকে, বামপন্থীরা এখনো পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য বিকল্প কর্মসূচি বা নতুন চিন্তাধারা হাজির করতে পারেনি—পুরোনো, ব্যয়বহুল সামাজিক গণতন্ত্রের পুনরাবৃত্তি ছাড়া।
এই ধারণাগত শূন্যতা ক্ষতিকর, কারণ যেমন অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা প্রয়োজন, তেমনি চিন্তার জগতেও। আর আজ আমরা এমন এক সময়ের মুখোমুখি, যখন চিন্তার প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে জরুরি—কারণ বর্তমান বৈশ্বিক পুঁজিবাদ উদার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ক্ষয় করছে।
গণতান্ত্রিক ঢেউ
কার্ল মার্কস যেমন বলেছিলেন, সামাজিক শক্তি ও পরিস্থিতি কোনো মতবাদকে সরাসরি “নির্ধারণ” করে না; তবে কোনো ধারণা তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তা সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আজ বিশ্বের অনেক জায়গায় উদার গণতন্ত্র হলো ডিফল্ট বা প্রাধান্যশীল মতবাদ—কারণ এটি নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই কাঠামোগুলোর পরিবর্তন যেমন নতুন মতাদর্শ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি মতাদর্শের পরিবর্তনও সমাজের কাঠামো বদলে দিতে পারে।
গত তিনশ বছর পর্যন্ত মানবসমাজে যে সমস্ত শক্তিশালী ধারণা সমাজ গঠন করেছে, তার প্রায় সবকটিই ছিল ধর্মীয় প্রকৃতির—চীনের কনফুসীয় মতবাদ ছাড়া। প্রথম যে বৃহৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বিশ্বজুড়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলে, সেটি ছিল উদারতাবাদ (Liberalism)। এটি ইউরোপের কিছু অঞ্চলে বাণিজ্যিক ও পরে শিল্পোন্নত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের সঙ্গে যুক্ত সপ্তদশ শতকের মতবাদ। (“মধ্যবিত্ত শ্রেণি” বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে এমন এক শ্রেণি, যারা আয়ের দিক থেকে সমাজের একেবারে শীর্ষে বা নিচে নয়; অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েছে এবং যাদের নিজস্ব সম্পত্তি, টেকসই দ্রব্য বা ব্যবসা রয়েছে।)
জন লক, মন্টেস্কিউ ও জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো ক্লাসিক চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যায়, উদারতাবাদ বলছে—রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ভর করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার সক্ষমতার ওপর, এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অবশ্যই আইনের দ্বারা সীমিত হতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ছিল এর অন্যতম মৌলিক নীতি। ইংল্যান্ডের গ্লোরিয়াস রেভলিউশন (১৬৮৮–৮৯) আধুনিক উদারতাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ এটি প্রথম সংবিধানগতভাবে স্থির করে দেয় যে—রাষ্ট্র নাগরিকদের সম্মতি ছাড়া বৈধভাবে কর আরোপ করতে পারে না।
প্রাথমিক পর্যায়ে উদারতাবাদ মানেই ছিল না গণতন্ত্র। ১৬৮৯ সালের সাংবিধানিক সমঝোতা যারা সমর্থন করেছিল, সেই হুইগরা সাধারণত ইংল্যান্ডের ধনী ভূমির মালিক শ্রেণির লোক ছিলেন; সেই সময়ের পার্লামেন্টে দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও কম মানুষ প্রতিনিধিত্ব পেতেন। অনেক ক্লাসিক উদারতাবাদী চিন্তাবিদ—মিলসহ—গণতন্ত্র সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা ও সমাজে অংশীদারিত্ব (অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকানা) আবশ্যক।
উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপজুড়ে ভোটাধিকার সীমিত ছিল—সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে।
১৮২৮ সালে অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া এবং পরে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের জন্য ভোটাধিকারে সম্পত্তি-নির্ভর শর্ত তুলে দেওয়া ছিল গণতান্ত্রিক নীতির এক প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয়।
ইউরোপে জনগণের বিশাল অংশের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং শিল্পশ্রমিক শ্রেণির উত্থান—এই দুই প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয় মার্কসবাদ জন্মের জন্য। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়—সেই একই বছরে ইউরোপের প্রায় সব বড় দেশে (যুক্তরাজ্য বাদে) বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় থেকেই শুরু হয় শতাব্দীব্যাপী প্রতিযোগিতা—একদিকে মার্কসবাদীরা, যারা “প্রক্রিয়াগত গণতন্ত্র” (একাধিক দল ও নির্বাচন) ত্যাগ করে “বস্তুনিষ্ঠ গণতন্ত্র” (অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল; অন্যদিকে উদার গণতান্ত্রিকরা, যারা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু একই সঙ্গে আইনের শাসন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সুরক্ষা বজায় রাখতে চেয়েছিল।
মূল প্রশ্ন ছিল—শিল্পশ্রমিক শ্রেণি কার পক্ষে দাঁড়াবে?
প্রাথমিক মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করতেন, তারা সংখ্যার জোরে জয়ী হবে। উনিশ শতকের শেষভাগে ভোটাধিকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টি ও জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যবাহী উদারপন্থীদের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করে।
তবে এই উত্থান প্রায়ই সহিংস প্রতিরোধের মুখে পড়ে; অনেক সময় কর্তৃত্ববাদী শাসকরা গণতন্ত্রকে দমন করেন, এবং প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিস্ট ও কিছু সমাজতন্ত্রী সরাসরি ক্ষমতা দখলের পথ বেছে নেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ত্যাগ করে।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/ziudbqt22.jpeg'>
সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন
বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে প্রগতিশীল বামপন্থী মহলে এক ধরনের ঐকমত্য গড়ে ওঠে যে—উন্নত সব দেশে একদিন না একদিন কোনো না কোনো রূপের সমাজতন্ত্র (অর্থাৎ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, যাতে সম্পদের বণ্টন সমানভাবে হয়) অনিবার্য হয়ে উঠবে।
রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ জোসেফ শুম্পিটারও তাঁর ১৯৪২ সালের বিখ্যাত গ্রন্থ Capitalism, Socialism and Democracy-তে লিখেছিলেন—“সমাজতন্ত্র একদিন জয়ী হবে, কারণ পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই সাংস্কৃতিকভাবে আত্মবিধ্বংসী।” তখনকার ধারণা ছিল, সমাজতন্ত্র আধুনিক সমাজের বিপুল জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও স্বার্থেরই প্রতিফলন।
কিন্তু রাজনীতি ও যুদ্ধের ক্ষেত্রের এই মতাদর্শিক সংঘাত চলার সময়, সমাজের ভিতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল যা মার্কসবাদী কল্পনাকে ভেঙে দেয়।
প্রথমত, শিল্পশ্রমিক শ্রেণির বাস্তব জীবনমান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে—এমনকি বহু শ্রমিক বা তাঁদের সন্তানরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করতে শুরু করে।
দ্বিতীয়ত, শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা ক্রমে স্থিতিশীল হয়ে পড়ে, এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা হ্রাস পেতে থাকে—কারণ সেবাখাত (service sector) ধীরে ধীরে উৎপাদনশিল্পকে প্রতিস্থাপন করে।
তৃতীয়ত, শিল্পশ্রমিক শ্রেণির নিচে নতুন এক দরিদ্র বা বঞ্চিত শ্রেণি গড়ে ওঠে—বর্ণ ও জাতিগত সংখ্যালঘু, অভিবাসী, নারী, সমকামী ও প্রতিবন্ধীদের মতো নানা সামাজিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে।
এই পরিবর্তনের ফলে উন্নত দেশগুলিতে ঐতিহ্যবাহী শ্রমিক শ্রেণি এক বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীতে পরিণত হয়—যারা অতীতের অর্জন রক্ষা করতে ইউনিয়নের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে থাকে।
শ্রেণি-রাজনীতির ব্যর্থতা
অর্থনৈতিক শ্রেণি যে রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য শক্তিশালী পতাকা হতে পারে—এই ধারণাটিই পরে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ১৯১৪ সালে ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণি যখন শ্রেণি-সংগ্রামের আহ্বান উপেক্ষা করে নিজ নিজ দেশের রক্ষণশীল নেতাদের পেছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ সমর্থন করল, তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (Second International)-এর জন্য এটি ছিল এক কঠোর শিক্ষা।
বিদ্বান আর্নেস্ট গেলনার এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটিকে বলেন “Wrong Address Theory”—
যেমন কিছু উগ্র শিয়া মুসলমান বিশ্বাস করেন, ফেরেশতা জিবরাইল ভুলবশত বার্তাটি মুহাম্মদকে দিয়েছেন, যদিও সেটি ছিল আলির জন্য, তেমনি মার্কসবাদীরাও মনে করেন—ইতিহাসের আত্মা বা মানবচেতনা ভুল ঠিকানায় পৌঁছেছে; বার্তাটি ছিল শ্রেণির জন্য, কিন্তু তা পৌঁছে গেছে জাতির কাছে।
গেলনারের মতে, ধর্ম যেমন মধ্যপ্রাচ্যে জাতীয়তাবাদের মতো সংগঠক শক্তি হিসেবে কাজ করে, তেমনি ইউরোপে জাতীয়তাবাদ মানুষের আত্মিক ও আবেগিক অনুভূতিকে স্পর্শ করেছিল—যা শ্রেণি-চেতনা কখনোই করতে পারেনি।
মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিজয়
মার্কস মনে করেছিলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি (বিশেষত পুঁজির মালিক বুর্জোয়া শ্রেণি) সবসময় একটি ক্ষুদ্র, সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু হিসেবেই থাকবে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল তা উল্টো—বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি আধুনিক উন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যার বৃহৎ অংশে পরিণত হলো। এই অবস্থায় সমাজতন্ত্র সমস্যায় পড়ে যায়।
এরিস্টটল থেকে শুরু করে বহু চিন্তাবিদ বিশ্বাস করতেন যে—স্থিতিশীল গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো একটি প্রশস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। যেখানে চরম ধনী ও চরম দরিদ্র—উভয় শ্রেণির আধিপত্য নেই, সেখানেই স্থিতিশীলতা সম্ভব। যখন উন্নত বিশ্ব সফলভাবে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে তুলল, তখন মার্কসবাদের আবেদন হারিয়ে গেল। আজও কেবলমাত্র যেখানে চরম বৈষম্য বিরাজমান—যেমন লাতিন আমেরিকার কিছু অঞ্চল, নেপাল, বা ভারতের পূর্বাঞ্চলের দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে—সেখানেই বামপন্থী র্যাডিকাল আন্দোলন টিকে আছে।
তৃতীয় গণতান্ত্রিক ঢেউ
রাজনৈতিক বিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত পরিভাষায় যেটিকে বলেছিলেন “তৃতীয় ঢেউ” (The Third Wave of Democratization)—
এই ঢেউ শুরু হয় ইউরোপের দক্ষিণাংশে ১৯৭০-এর দশকে এবং চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম পতনের মাধ্যমে।
১৯৭০ সালে পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫টি; ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২০টিরও বেশি।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দেয় ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কের মতো দেশে। অর্থনীতিবিদ মোইসেস নাইমের ভাষায়, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি—
- তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত,
- সম্পত্তির মালিক,
- প্রযুক্তিগতভাবে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত,
- এবং রাজনৈতিকভাবে দাবি-দাওয়া জানাতে সক্ষম।
তাদের প্রত্যাশা ও প্রযুক্তিগত সংযোগের কারণে সরকারগুলোর প্রতি তাদের চাপ সৃষ্টি হয়।
আরব বসন্তের (Arab Spring) সূচনা করেছিল মূলত এই নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত তিউনিসিয়ান ও মিশরীয় যুবকরা—যারা চাকরি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল একনায়কতান্ত্রিক শাসনে।
চলবে ...............
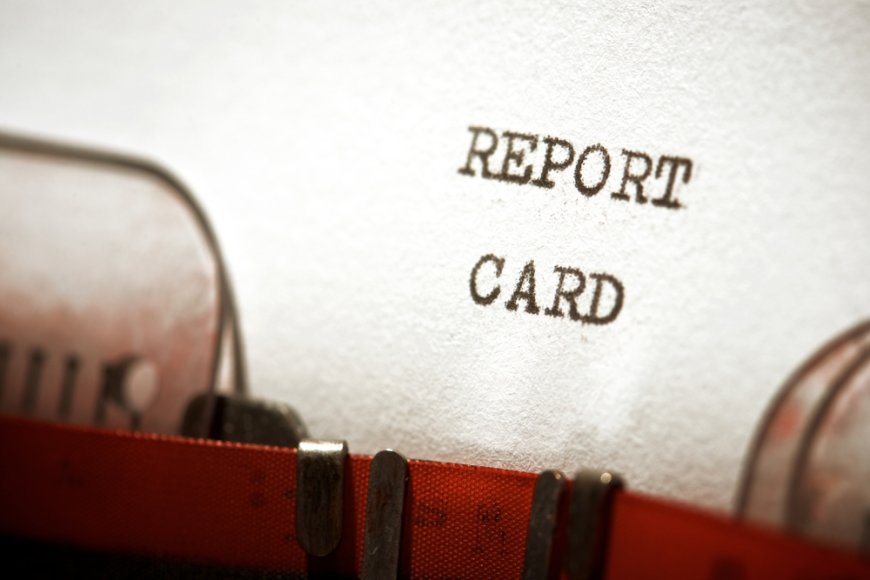


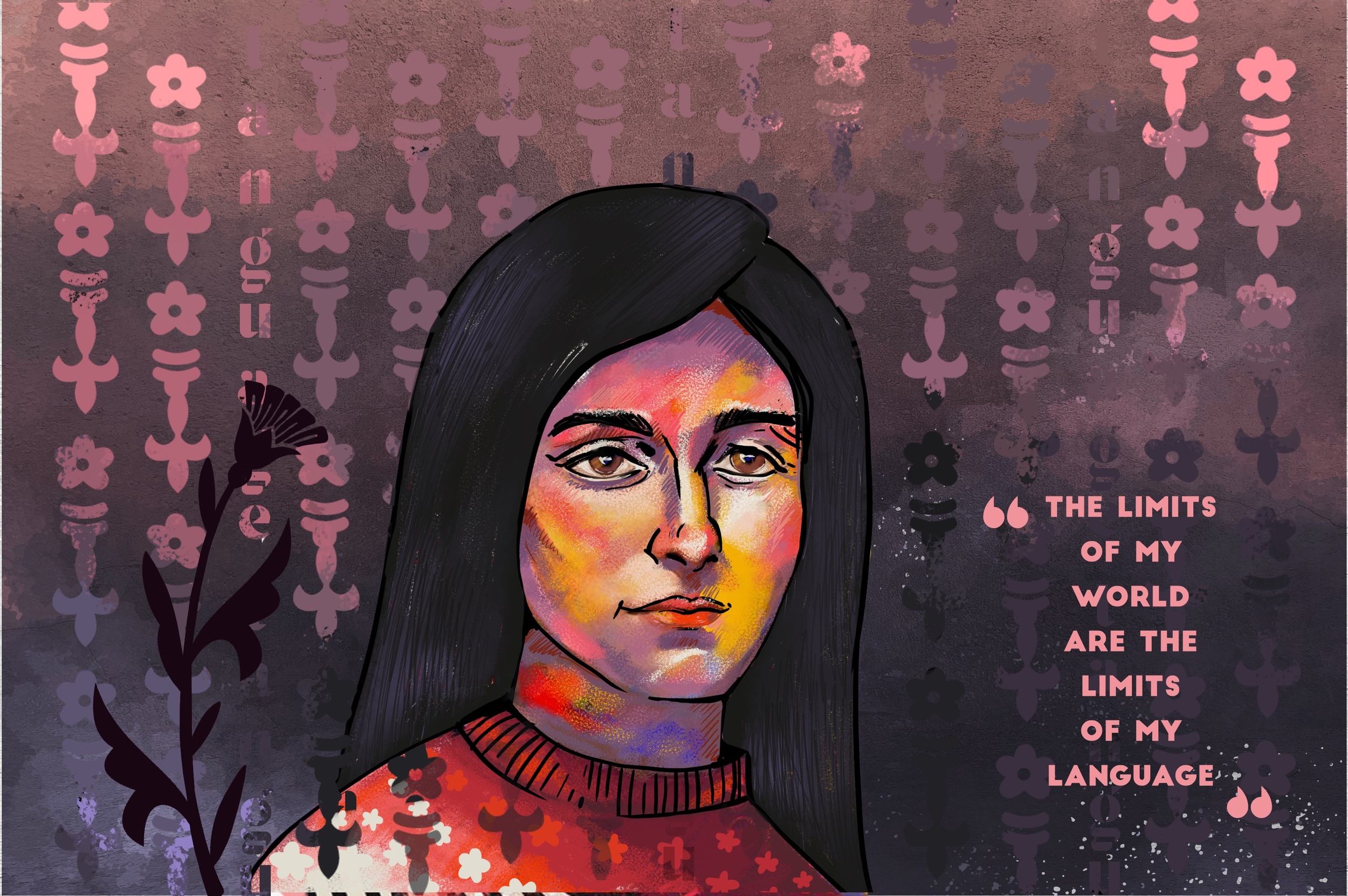



Comments