২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেমন বদলে দিয়েছে, তেমনি দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানে একটি মৌলিক পুনর্বিন্যাসের সুযোগ তৈরি করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মাধ্যমে উদ্ভূত রাজনৈতিক শূন্যস্থান শুধু দেশীয় শক্তিসংঘাতকেই নতুন দিক দেয়নি—এটি দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য পুনঃনির্ধারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বিরল জানালা উপহার দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা–ওয়াশিংটন সম্পর্ক বর্তমানে একটি নীতিগত, কৌশলগত এবং আদর্শভিত্তিক পুনর্গঠন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।
১৫ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেশনাল ব্রিফিং—যা ছিল বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক আইনপ্রণেতা-স্তরের আলোচনা—এই পরিবর্তনের দিক ও চরিত্রকে আরও দৃশ্যমান করে। এই অনুষ্ঠান দেখিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র এখন বাংলাদেশের প্রতি তার নীতি পুনর্বিবেচনা করতে ইচ্ছুক, শুধু দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক কারণে নয়—বরং মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারকেন্দ্রিক নতুন কূটনৈতিক আচরণের প্রতিশ্রুতি থেকে।
শেখ হাসিনা পরবর্তী যুগ: যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কৌশলগত হিসাব
গত এক দশকে বাংলাদেশ গণতন্ত্রহীনতা, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা, জবাবদিহির অভাব এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নজরে একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিল। ওয়াশিংটন বারংবার মূল্যবোধ-ভিত্তিক কূটনীতির আহ্বান জানালেও শেখ হাসিনা সরকারের প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভারতের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা, এবং জিও-স্ট্র্যাটেজিক অগ্রাধিকারের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ছিল সীমাবদ্ধ অবস্থানে।
কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি মৌলিকভাবে বদলেছে। যুক্তরাষ্ট্র—বিশেষত কংগ্রেস—এখন বাংলাদেশকে তিনটি কৌশলগত অক্ষের মাধ্যমে দেখছে:
১) মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন,
২) চীন–মার্কিন প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতি,
৩) বাণিজ্য ও শ্রম অধিকার-সংকট মোকাবিলা।
এই কারণে ঢাকা–ওয়াশিংটন সম্পর্ক এখন আর একমুখী নয়; এটি পারস্পরিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে দাঁড়াতে শুরু করেছে।
কংগ্রেসম্যান লয়েড ডগেট ও জিম ম্যাকগাভার্নের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের প্রতি অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। শুধু রাজনৈতিক ভাষণের জায়গা থেকে নয়—এটি এখন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির enforceable শর্ত।
বাংলাদেশের জন্য এর অর্থ হলোঃ
যদি অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার না করে, নিরাপত্তা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে, এবং নির্বাচন ও বিচারব্যবস্থার সংস্কার বাস্তবায়ন না করে—তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ রাজনৈতিক সমর্থন আসবে না।
শেখ হাসিনা পরবর্তী রাজনৈতিক স্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের চোখে একটি “test case”—যেখানে দেখা হবে, দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র কি সত্যিই পুনর্নির্মাণযোগ্য। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ভারত-নির্ভর ছিল। দিল্লি ছিল বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রধান তথ্যদাতা। কিন্তু জুলাই বিপ্লব যুক্তরাষ্ট্রকে দেখিয়েছে—বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক রূপান্তর ভারতের প্রভাবের বাইরে ঘটে যেতে পারে এবং বাস্তবে ঘটেছে।
এই কারণে ওয়াশিংটন এখন দুইটি নতুন বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে:
১. বাংলাদেশকে মূল্যবোধ-ভিত্তিক স্বাধীন actor হিসেবে দেখা।
২. বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি কূটনৈতিক, নীতিগত ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গঠন।
এটি ভারতের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা; বাংলাদেশ আর কেবল একটি নিরাপত্তা-জটপাকানো সীমান্তরাষ্ট্র নয়—এটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র।
বাংলাদেশের চীনের প্রতি নির্ভরশীলতা—ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্সিং, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, বাণিজ্য—যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্বেগ।
জুলাই বিপ্লবের ফলে ব্যালান্স-অফ-পাওয়ার পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হলেও, চীনের অর্থনৈতিক উপস্থিতি ওয়াশিংটনের নীতি-নির্ধারকদের জন্য এখনো চ্যালেঞ্জ।
কংগ্রেসের আলোচনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে: বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে “non-extractive, equitable, and rights-centric।” এর অর্থ—ব্যবসা বা নিরাপত্তা সহযোগিতা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিনিময়ে হবে না; আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্মান ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে।
ডায়াসপোরার ভূমিকা: পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন শক্তি
বাংলাদেশি ডায়াসপোরা এখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কেবল remittance-sender নয়—policy influencer।
ডায়াসপোরা-নেতৃত্বাধীন থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক, মানবাধিকার গ্রুপ, শিক্ষাবিদ ও নীতিবিশ্লেষকদের অংশগ্রহণ দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের কূটনীতি এখন বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তরীয়।
এই নতুন diaspora diplomacy যুক্তরাষ্ট্রকে শেখ হাসিনা আমলের তথ্য-অবরোধের বাইরে এনে বাংলাদেশ সম্পর্কে স্বাধীন, দক্ষ এবং তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ দিচ্ছে।
সামনের পথ: সুযোগ ও ঝুঁকি
ঢাকা–ওয়াশিংটন সম্পর্ক এখন এক সংকটময় কিন্তু সম্ভাবনাময় মোড়ে দাঁড়িয়ে।
সুযোগ:
গণতান্ত্রিক সংস্কার সফলভাবে অগ্রসর হলে বাংলাদেশ–মার্কিন সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে গভীর হতে পারে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হলে নিরাপত্তা সহযোগিতা থেকে শুরু করে বাণিজ্য ও শ্রম অধিকার—সব ক্ষেত্রেই দুই দেশের মধ্যে সমন্বয় নতুন মাত্রা পাবে। এর ফলে বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একইসঙ্গে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পুনরায় গতি ফিরে পেতে পারে, কারণ আন্তর্জাতিক বাজার সাধারণত স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বেশি আস্থার সঙ্গে মূল্যায়ন করে। তদুপরি, যদি বাংলাদেশ একটি নতুন, স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়া শুধু সম্ভাব্য নয়—বরং প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠবে
ঝুঁকি:
ঢাকা–ওয়াশিংটন সম্পর্কের সামনের পথ যতটা সম্ভাবনাময়, ততটাই ঝুঁকিপূর্ণ। সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা বা দমননীতির পুনরাবৃত্তি, যা শুধু অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকেই বাধাগ্রস্ত করবে না, বরং যুক্তরাষ্ট্রের আস্থা ও সমর্থনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। একইসঙ্গে চীন–যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতার তীব্রতর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ যদি কৌশলগতভাবে প্রস্তুত না থাকে, তবে দেশটি দুই পরাশক্তির চাপ ও প্রত্যাশার মধ্যে নীতিগত ভারসাম্য রক্ষা করতে সমস্যায় পড়বে। রোহিঙ্গা সংকটের অব্যাহত স্থবিরতাও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের একটি জটিল মাত্রা তৈরি করে—মানবাধিকার ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার এই বহুমাত্রিক সংকটের সমাধান ছাড়া বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে। এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অযোগ্যতা সংস্কার বাস্তবায়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধা দিতে পারে, যা যে কোনো দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও কূটনৈতিক আস্থার পথে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে।
জুলাই বিপ্লব যে নতুন রাজনৈতিক দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যুক্তরাষ্ট্র সেই দিগন্তকে বাস্তবায়নে আগ্রহী কিন্তু সতর্ক। ঢাকা–ওয়াশিংটন সম্পর্ক এখন এমন একটি পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যেখানে উভয় দেশের সিদ্ধান্ত তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। বাংলাদেশ যদি গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও মানবাধিকারের পথে অটল থাকে—তাহলে এই সম্পর্ক শুধু পুনর্গঠিত হবে না, ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই অংশীদারত্বে পরিণত হবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম এখন শুধু একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়—এটি দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির ভবিষ্যৎ, বৈশ্বিক মূল্যবোধের পরীক্ষা, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা।
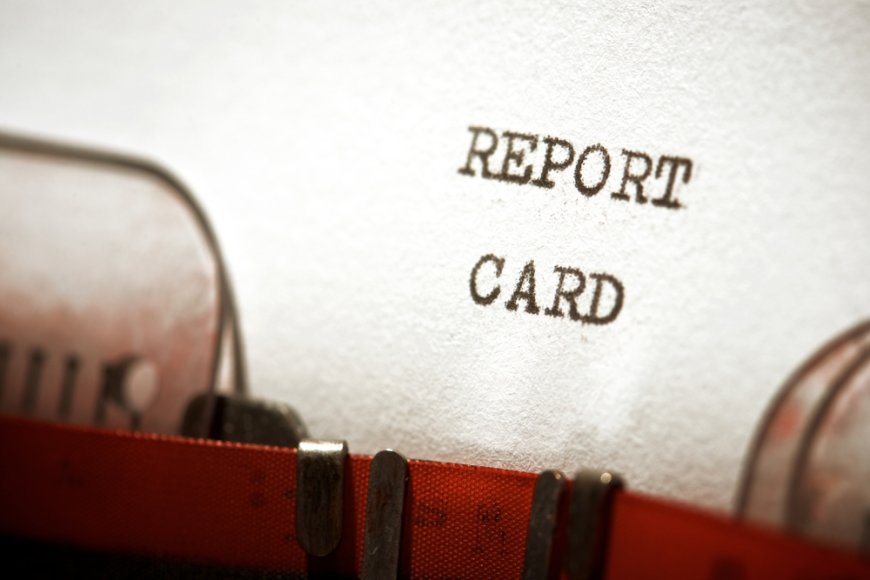


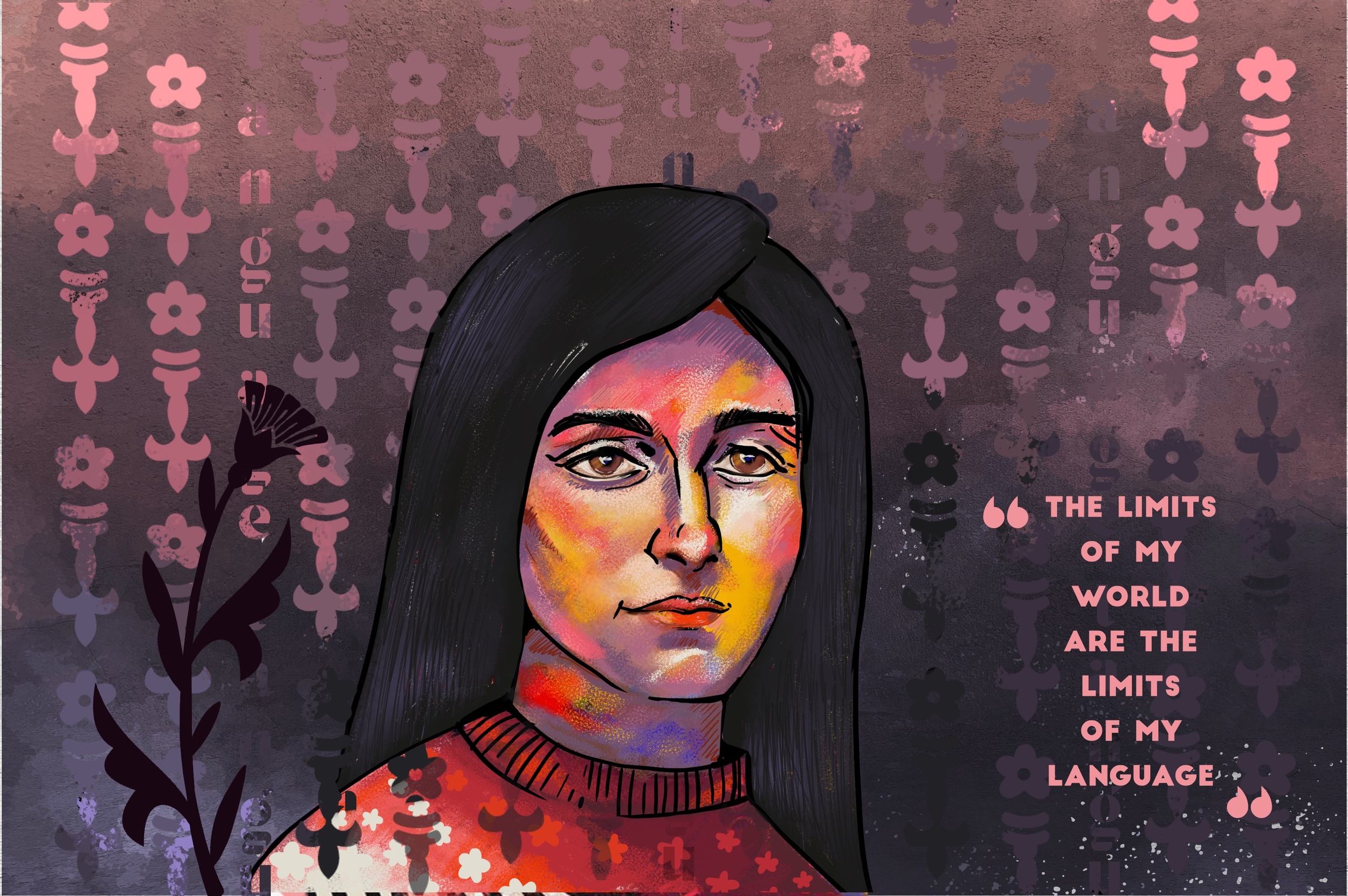



Comments