বিশ্বজুড়ে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ডানদিকে। ঢাকা থেকে লন্ডন পর্যন্ত—জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা এবং কঠোর আইন-শৃঙ্খলা নীতির প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দলগুলো এখন নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি: জনমতের স্রোত আর আগের মতো নেই, এবং ‘লিবারেল’ বা উদারনৈতিক রাজনীতির জায়গা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে।
বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। সম্প্রতি ডানপন্থী ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির দেশের দুইটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছে। এর পর থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক—এটা কি বাংলাদেশের তরুণদের নতুন রাজনৈতিক মনোভাবের প্রতিফলন, নাকি হতাশ জনগণের একটি তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ?
অনেক কথিত ‘জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষক’ এখন বলছেন, বাংলাদেশের উদারনৈতিক ও মধ্যপন্থী দলগুলোর উচিত ইসলামপন্থী আদর্শের কিছু উপাদান গ্রহণ করা, যাতে তারা জনগণের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন মূলধারার দল কখন ইসলাম-বিরোধী অবস্থান নিয়েছে? এমন একটি দেশে, যেখানে প্রায় পুরো জনগোষ্ঠী মুসলমান, সেখানে ইসলামের নামে রাজনীতি করা আসলে ভোট ব্যাংকের খেলাই নয় কি?
আর প্রবাসে বসে যারা লিবারেল পার্টিকে আদর্শগত সমঝোতার পরামর্শ দিচ্ছেন, তারা নিজের দেশের রাজনীতিতে কেমন ভূমিকা রাখছেন—সেটাও ভেবে দেখা দরকার।
এখানেই বাংলাদেশের রাজনীতির গভীর সংকটটি স্পষ্ট হয়: উদারনৈতিক দলগুলোর সামনে এখন দ্বিধা—তারা কি আদর্শে আপস করবে, নাকি নীতিগত অবস্থান আরও দৃঢ় করবে?
বাংলাদেশ এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এক দশকেরও বেশি সময় পর এখানে প্রথমবারের মতো একটি নতুন রাজনৈতিক সূচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসনের দীর্ঘ পর্বের পর নাগরিকরা এখন জবাবদিহি, ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রত্যাশা করছে—যেখানে ক্ষমতা জনগণের সেবায় ব্যবহৃত হবে, কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। কিন্তু এ সুযোগ তৈরি হতেই পুরনো প্রলোভনগুলো আবার ফিরে এসেছে—জনতাবাদী ভাষণ, ধর্মভিত্তিক বিভাজন, এবং কঠোরতা প্রদর্শনের রাজনীতি।
এই প্রবণতা শুধু বাংলাদেশের নয়। ভারতের উদাহরণটা এখন চোখে পড়ার মতো। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিকে মিশিয়েছে আক্রমণাত্মক সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী রাজনীতির সঙ্গে। বিরোধী দলগুলো ভোট হারানোর ভয়ে প্রায়ই হিন্দুত্ববাদী বক্তব্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পায়নি। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) কিংবা নাগরিক তালিকা (NRC)-এর মতো বিভাজনমূলক নীতির প্রতিরোধে বিরোধীরা একত্র হতে ব্যর্থ হয়েছে।
পশ্চিমা বিশ্বেও একই চিত্র। যুক্তরাজ্যে ২০২৪ সালে “Unite the Kingdom” নামে ডানপন্থী অভিবাসনবিরোধী মিছিল রাস্তায় নামলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ায় “March for Australia” শিরোনামে হওয়া বিক্ষোভে পুলিশকে টিয়ার গ্যাস ও পেপার স্প্রে ব্যবহার করতে হয়েছে। ইউরোপজুড়ে এখনো চলছে ইইউ’র অভিবাসন ও আশ্রয় চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।
এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বনেতারা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার ২০২৪ সালের অভিবাসনবিরোধী দাঙ্গাকে কঠোরভাবে নিন্দা করে ইউরোপীয় প্রগতিশীলদের সঙ্গে যৌথভাবে ডানপন্থী চরমপন্থা মোকাবিলার আহ্বান জানান। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভগুলোকে “ঘৃণার রাজনীতি” বলে উল্লেখ করেন এবং সতর্ক করেন যে, নব্য নাৎসি গোষ্ঠী জনমতের ভয়কে কাজে লাগাচ্ছে। অন্যদিকে, ভারতের মোদি সরকারকে অভিযোগ করা হয়, তারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা ডানপন্থী রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে—যদিও মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রী নিজে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে শান্তির আহ্বান জানান।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি মধ্যপন্থী ও লিবারেল দলগুলোও ডানপন্থী ভাষা ও কৌশল অনুকরণ শুরু করে—যেমন নৈতিক পুলিশি আচরণ, ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার বা কঠোর শাস্তির ডাক—তাহলে গণতন্ত্রের চক্র আবারও একই জায়গায় ফিরে যাবে, শুধু মুখ বদলাবে।
জনতাবাদী শর্টকাট হয়তো স্বল্পমেয়াদে ভোট এনে দিতে পারে, কিন্তু এটি দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রকে ফাঁপা করে তোলে। যখন প্রতিটি দল “অধিক দেশপ্রেমিক” বা “অধিক ধার্মিক” প্রমাণে প্রতিযোগিতা শুরু করে, তখন ভিন্নমত প্রকাশের জায়গা সংকুচিত হয়, সংখ্যালঘু ও নারীদের অংশগ্রহণ কমে যায়, এবং সমাজে বিভাজন আরও গভীর হয়।
বাংলাদেশ এখন একটি মৌলিক সিদ্ধান্তের মুখে দাঁড়িয়ে আছে—এ দেশ কি নীতিনিষ্ঠ, বহুত্ববাদী রাজনীতি বেছে নেবে, নাকি আবারও ধর্ম ও পরিচয়ের রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে?
সত্যিকারের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ হবে তখনই, যখন ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং ক্ষমতার ব্যবহারের ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যারা সবচেয়ে অবহেলিত, নিপীড়িত, এবং কণ্ঠহীন—তাদের জন্য ন্যায় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই হবে নতুন রাজনীতির লক্ষ্য।
এক দশক ধরে যে রাষ্ট্র কাঠামো দমননীতির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেই কাঠামো ভাঙার সুযোগ এখনই। কিন্তু যদি এই পরিবর্তনের হাওয়ায় আবারও ধর্ম, জাতীয়তাবাদ বা শাস্তিমূলক রাজনীতি ঢুকে পড়ে, তাহলে এই সম্ভাবনা ভেস্তে যাবে।
রাজনীতির আসল পরীক্ষা হবে কে ক্ষমতায় আসে, তা নয়—বরং ক্ষমতায় থেকে কে নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনর্গঠন করে, এবং বাংলাদেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়নিষ্ঠ ও সহনশীল রাষ্ট্রে পরিণত করে।
এখনই সময় গ্যালারির জন্য অভিনয় বন্ধ করে সত্যিকারের দেশ গঠনের রাজনীতি শুরু করার।
(প্রায় ১,০০০ শব্দ)
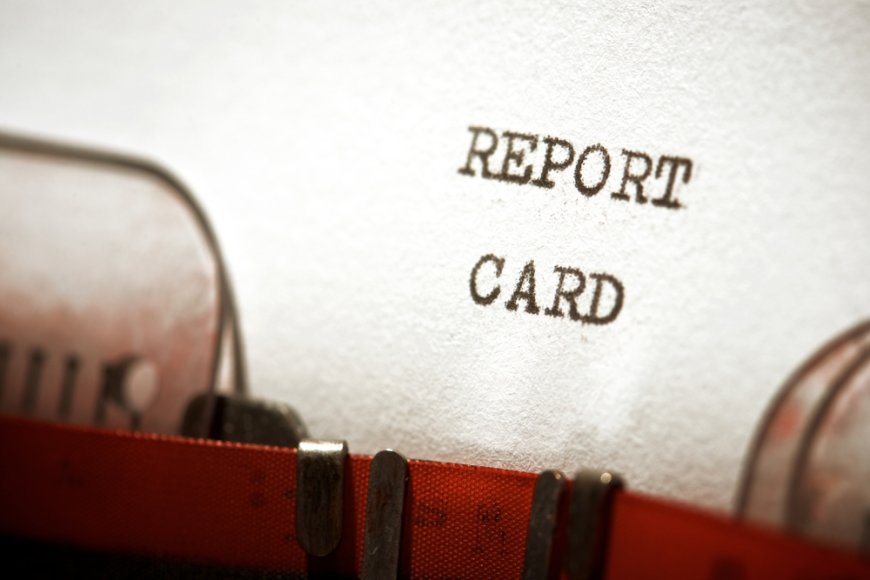


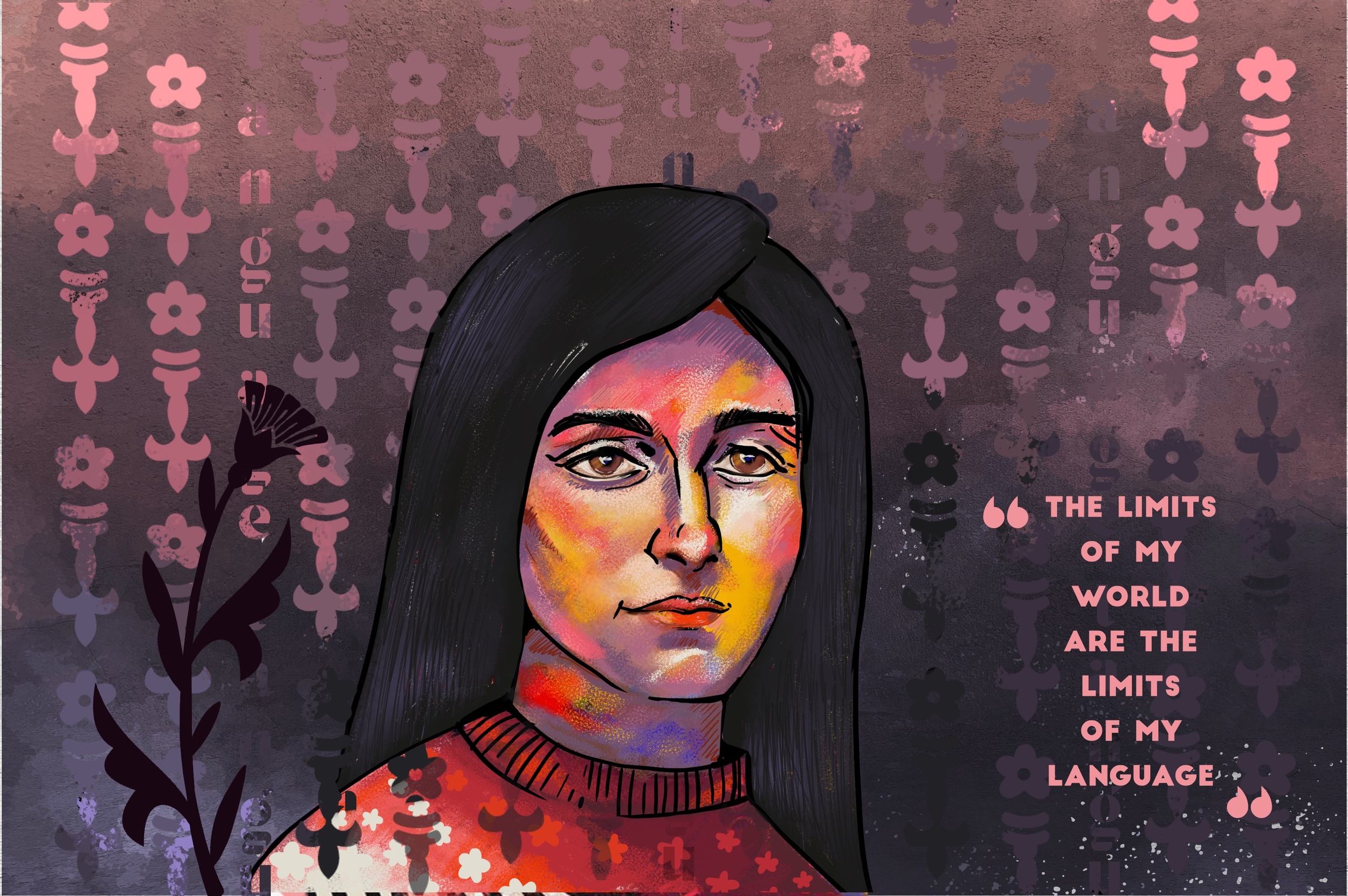



Comments