দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ইতিহাসে নেপাল সবসময়ই এক ব্যতিক্রমী পরীক্ষাগার। রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্র, তারপর সাংবিধানিক গণতন্ত্রে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেশটি একাধিক ধাপ অতিক্রম করেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে Gen Z—যারা ইন্টারনেট, মোবাইল, সামাজিক মাধ্যমের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে—তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। তারা ক্রমশ দুর্নীতি, নেপোটিজম, বেকারত্ব ও রাজনৈতিক অচলাবস্থায় হতাশ হয়ে উঠছিল। সেই জমে থাকা ক্ষোভ হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটাল সেপ্টেম্বরে, যখন সরকার সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।
২০২২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর নেপাল একটি ঝুলন্ত সংসদ পায়। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় প্রধান দলগুলোকে জোট সরকার গঠনের পথে হাঁটতে হয়। শুরুতে নেপালের দুটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি—কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মাওবাদী সেন্টার) এবং নেপালি কংগ্রেস—মিলে সরকার গঠন করে। মাওবাদী নেতা পুষ্পকমল দাহাল, যিনি ‘প্রচণ্ড’ নামেই বেশি পরিচিত, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। তবে নেপালের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জোটগুলো খুব কম সময়ই টেকে।
প্রথমদিকে প্রচণ্ড নেতৃত্বাধীন সরকার সংস্কারমুখী বক্তব্য দিলেও বাস্তবে তাদের নীতিনির্ধারণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ নানা সমালোচনার জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অঙ্গীকার সত্ত্বেও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, যুবকদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি এবং ফেডারেল কাঠামোকে শক্তিশালী করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সরকার পিছিয়ে পড়ে। এরই ফলে জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে, তীব্র হতাশা তৈরি হয়।
অর্থনীতির মন্দা, বেকারত্ব, এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা নেপালের সমাজকে ক্রমশ ভঙ্গুর করে তোলে। শিক্ষা শেষ করেও হাজার হাজার তরুণ চাকরি না পেয়ে বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বিদেশ থেকে প্রবাসী আয়ের টাকায় অর্থনীতি কিছুটা সচল থাকলেও দেশের ভেতরে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে সরকারের দুর্বল নীতি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বড় ভূমিকা রাখছে।
সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত আরও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কর আরোপের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকা, জনসেবামূলক খাতে দুর্নীতি, এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্যমূলক নীতির কারণে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়। একইসঙ্গে অবকাঠামো উন্নয়নের নামে অনেক প্রকল্পে অনিয়ম ও অর্থ অপচয়ের অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে চীনের সঙ্গে অবকাঠামো বিনিয়োগ এবং ভারতের সঙ্গে সীমান্ত রাজনীতি—দুটিই সরকারের জন্য ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।
বর্তমানে প্রচণ্ড নেতৃত্বাধীন সরকার সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখলেও রাজনৈতিক মেরুকরণ তীব্র। নেপালি কংগ্রেস একদিকে সরকারকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে, অন্যদিকে ক্ষমতায় বেশি ভাগীদারি চাইছে। অপরদিকে, বিরোধীদলীয় নেতা কে.পি. শর্মা ওলি সরকারবিরোধী বক্তব্য দিয়ে জনসমর্থন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতিতে নেপালের তরুণ প্রজন্ম—বিশেষ করে জেনারেশন জেড—নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তারা রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে এবং নতুন রাজনৈতিক বিকল্পের খোঁজ করছে।
২০২৪ সালের ১২ জুলাই প্রচণ্ড সংসদের আস্থা ভটে পরাজিত হয়ে পদত্যাগ করেন কেপি শর্মা অলি ১৪ জুলাই ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন এবং ১৫ জুলাই তার নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নেই। এই সরকারটি “চতুর্থ Oli সরকার” হিসেবে পরিচিত। এই নতুন সরকার দ্রুত পার্লামেন্টে ভোটে বিশ্বাস লাভ করে; Oli সরকার ২১ জুলাই ২০২৪-এ নিম্নকক্ষে ১৮৮ ভোট পায়, যা বিশ্লেষকদের মতে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিল। তিনি ঘোষণা দেন যে তার সরকার নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে—অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ, অভ্যন্তরীণ শিল্পায়ন, দারিদ্র্য ও দারুনতা হ্রাস, এবং দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।
নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো Oli সরকারের অধীনে সিদ্ধান্ত হিসেবে এসেছে বা বাস্তবায়ন হয়েছে:
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/87h13axuk.jpg'>
- গনতন্ত্র ও পার্টি রাজনীতি নিয়ে জনমত
- একটি জরিপ (International Republican Institute, IRI) দেখায় যে, জনসাধারণের মধ্যে এখনও গনতন্ত্রের প্রতি আস্থা রয়েছে, তবে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দায়িত্ব যথেষ্টভাবে পালন করছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ও আক্ষেপ বেশি। প্রায় ৫৯% লোক মনে করেন গনতন্ত্রই দেশটির জন্য সেরা সরকার ব্যবস্থা; কিন্তু প্রায় ৬২% মানুষ চান নতুন রাজনৈতিক দলগুলি তৈরি হোক, কারণ তারা বর্তমান দলগুলোর দায়িত্ব পালনে অব্যাহত ব্যর্থতা দেখছেন।
- পার্টির অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও Oli-এর বিরোধিতা
- Oli পার্টির অভ্যন্তরীণ ফ্র্যাকশন ও বিরোধ উভয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন। CPN-UML ভিতরেই Pushpa Kamal Dahal ও Madhav Kumar Nepal-এর অংশ Oli-এর কিছু সিদ্ধান্তকে “অবৈধ” বা “অসংবিধানিক” বলে সমালোচনা করছে, এমনকি পার্টির মেম্বারশিপ বাতিলের মতো সাংগঠনিক সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।
- রাজনৈতিক বিবাদ ও বিরোধীদলীয় চাপে টিকতে চাওয়া
- NC (Nepali Congress) পার্টি সরকারের অংশ হলেও তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে—কোন সিদ্ধান্তে আগ্রহ নেই, কখন বিরোধীদল হিসেবে অবস্থান নেওয়া হবে সে বিষয়ে অস্থায়ী উত্তেজনা আছে। Oli নিজে বেশ কিছুসময় বলছেন যে, সামান্য একটি ছোট সংখ্যালঘু অংশ এখনও “৫ শতাংশ” জনমতও পায় না যারা বিরোধীর ভূমিকা নিচ্ছে; তিনি মনে করছেন তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়া।
- বাজার ও অর্থনৈতিক চাহিদা
- অর্থনীতি ধীরে ধীরে সচল হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে ব্যাঙ্ক, রেমিটেন্স, পর্যটন—যেমন খাতগুলো—পুরনো সমস্যায় জর্জরিত। বিদেশে রেমিটেন্সে পতন, উন্নয়ন প্রকল্পে ধীরগতি ও বাজেট ঘাটতির প্রশ্ন বাড়ছে। Oli সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করা। (এই দিক থেকে স্পষ্টত অনেক বেশি রিপোর্ট প্রয়োজন)।
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে হঠাৎ সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত সেই ক্ষোভকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ রূপ নেয় সহিংস আন্দোলনে, রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে শুরু করে পোখরা, বিরাটনগর, ভিরাটজঙ্গ, জনকপুর, বীরগঞ্জসহ প্রায় সব বড় শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন শুধু একটি সরকারের পতন ঘটায়নি, বরং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নতুন এক শিক্ষার জন্ম দিয়েছে—ডিজিটাল যুগে তরুণদের উপেক্ষা করার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে।
প্রথমে বিষয়টি অনেকের কাছে তুচ্ছ প্রযুক্তিগত মনে হলেও তরুণদের কাছে এটি ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। নেপালের হাজার হাজার যুবক-যুবতী প্রতিদিন তাদের কাজ, পড়াশোনা, ব্যবসা, রাজনীতি এমনকি সামাজিক বন্ধনও সামাজিক মাধ্যমে গড়ে তুলেছিল। সেই প্ল্যাটফর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া। তাই ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা নামতেই তরুণদের ঢল নামে কাঠমান্ডুর মৈতিগর মণ্ডলায়। সেখানে তারা স্লোগান দেয়—“ডিজিটাল স্বাধীনতা চাই”—এবং রাতভর অবস্থান করে। পুলিশ প্রথম থেকেই কঠোরভাবে দমন করতে চায়। রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, এমনকি গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটে। সেদিনই অন্তত চারজন নিহত হয়, শতাধিক আহত হয়। আন্দোলনের প্রথম দিনেই প্রাণহানির ঘটনা আন্দোলনকে সীমিত দাবির বাইরে নিয়ে গিয়ে পুরো প্রজন্মের অস্তিত্বের লড়াইয়ে পরিণত করে।
পরদিন, ৯ সেপ্টেম্বর, বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর বাইরে। পোখরা, বিরাটনগর, বীরগঞ্জ—প্রায় সব বড় শহরেই তরুণরা রাস্তায় নামে। এদিন থেকে আন্দোলনের ধরন বদলে যায়। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ রূপ নেয় সহিংসতায়। কাঠমান্ডুর পার্লামেন্ট ভবনের কিছু অংশে আগুন লাগানো হয়, সরকারি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, দলীয় কার্যালয়ে হামলা হয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো তখনই নেপালকে “দক্ষিণ এশিয়ার নতুন বিপ্লবের মঞ্চ” বলে অভিহিত করতে শুরু করে।
১০ সেপ্টেম্বর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং রাজধানীতে কারফিউ জারি করে। সেনাবাহিনী রাস্তায় নামে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা পিছিয়ে যায়নি। তারা সরকারি দপ্তর ঘেরাও করে, কাগজপত্র বাইরে ফেলে আগুনে পোড়ায়। পোখরার পর্যটন এলাকা লেকসাইডে দোকানপাট ভাঙচুর হয়, পুরো পর্যটন ব্যবসা থমকে যায়। শিল্পাঞ্চল বিরাটনগরে শ্রমিকরাও আন্দোলনে যোগ দেয়, ফলে বিক্ষোভে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এদিন নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সাতাশে, আহত হয় প্রায় এক হাজার মানুষ। শহরজুড়ে ধোঁয়া, রক্ত ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
১১ সেপ্টেম্বর ঘটনাপ্রবাহ এক নতুন মোড় নেয়। রাষ্ট্রপতি সেনা প্রধান, প্রবীণ রাজনীতিক এবং কিছু তরুণ প্রতিনিধিকে ডেকে বৈঠক করেন। আলোচনায় উঠে আসে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশিলা কার্কির নাম অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী হিসেবে। রাজনৈতিক মহলে এই নাম দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পায়, কারণ তিনি অতীতে সৎ ও নিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একই দিনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের ঘোষণা দেন। আন্দোলনকারীরা এটিকে প্রথম বিজয় হিসেবে উদযাপন করে। রাজধানীর রাস্তায় আবারও হাজারো মানুষ জড়ো হয়ে নিহতদের স্মরণ করে, আতশবাজি ফোটায়, স্লোগান দেয়—“আমরা জিতেছি।” কিন্তু অনেকেই জানত, এ লড়াইয়ের প্রকৃত পরিণতি এখনো বাকি।
১২ সেপ্টেম্বর থেকে ধীরে ধীরে উত্তেজনা প্রশমিত হতে থাকে। কারফিউ আংশিকভাবে তুলে নেওয়া হয়, দোকানপাট খুলে যায়। আন্দোলনকারীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে নিহতদের স্মরণে প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তারা স্পষ্ট করে জানায়, তাদের লক্ষ্য এখন শুধু সামাজিক মাধ্যমের স্বাধীনতা নয়; দুর্নীতি ও নেপোটিজমের বিরুদ্ধে মৌলিক সংস্কার চাই। নিহতের সংখ্যা সরকারিভাবে তখন ৩৫, যদিও আন্দোলনকারীরা দাবি করে ষাটের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/slhdj2wr7.jpg'>
১৩ সেপ্টেম্বর পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত থাকে, তবে উত্তেজনা অটুট। বিভিন্ন শহরে আলোচনা সভা বসে। তরুণরা পাঁচ দফা দাবি প্রকাশ করে—দুর্নীতি দমন কমিশনের পুনর্গঠন, বেকারত্ব কমাতে তাৎক্ষণিক কর্মসূচি, ডিজিটাল স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, শিক্ষাখাতে সংস্কার এবং ছয় মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন। বিরাটনগরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ এই দাবিগুলোর পক্ষে সমর্থন জানায়। আন্দোলনের ভাষা আরও সংগঠিত হতে শুরু করে, যেন একটি রাজনৈতিক রূপরেখা তৈরি হচ্ছে।
১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, নেপালের পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এলেও অস্থিরতা পুরোপুরি কাটেনি। সেনাবাহিনী এখনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করছে। সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৩৮, আহত প্রায় এক হাজার। আন্দোলনকারীরা অবশ্য বলছে মৃত ষাটের বেশি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইতিমধ্যে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তরুণ নেতারা বলেছে—“এটাই কেবল শুরু, আমাদের লড়াই চলবে।”
এই পুরো প্রক্রিয়ায় কাঠমান্ডু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পার্লামেন্ট ভবন, প্রশাসনিক সদরদপ্তর Singha Durbar এবং পুলিশের সদর দপ্তর গুরুতর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে। সরকারি হিসাবে শুধু রাজধানীতেই অন্তত পঁচিশজন নিহত হয়েছে। পোখরার পর্যটন অঞ্চল প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিরাটনগরে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করেছে। সীমান্তঘেঁষা বীরগঞ্জে ভারত-নেপাল বাণিজ্য কয়েক দিন বন্ধ ছিল, ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি বেড়েছে।
এই আন্দোলনের মূল উৎস কেবল সামাজিক মাধ্যম নিষেধাজ্ঞা নয়। বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা দুর্নীতি, রাজনৈতিক পরিবারের কর্তৃত্ব, তরুণদের কর্মসংস্থানের অভাব এবং রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতা এ আন্দোলনের ভিত তৈরি করেছে। সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনা কেবল স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই আন্দোলন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ভারত সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে, চীন স্থিতিশীলতার আহ্বান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে। বিশ্ব গণমাধ্যম একে দক্ষিণ এশিয়ার “ডিজিটাল গণতন্ত্র আন্দোলন” আখ্যা দিয়েছে।
তবে এই আন্দোলনের দুর্বল দিকও স্পষ্ট। নেতৃত্বহীনতা একদিকে আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত করেছে, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সমাধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সহিংস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ আন্তর্জাতিক সহানুভূতি কমিয়ে দিতে পারে। তাই Gen Z-এর সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাদের সাফল্যকে টেকসই রূপ দেওয়া।
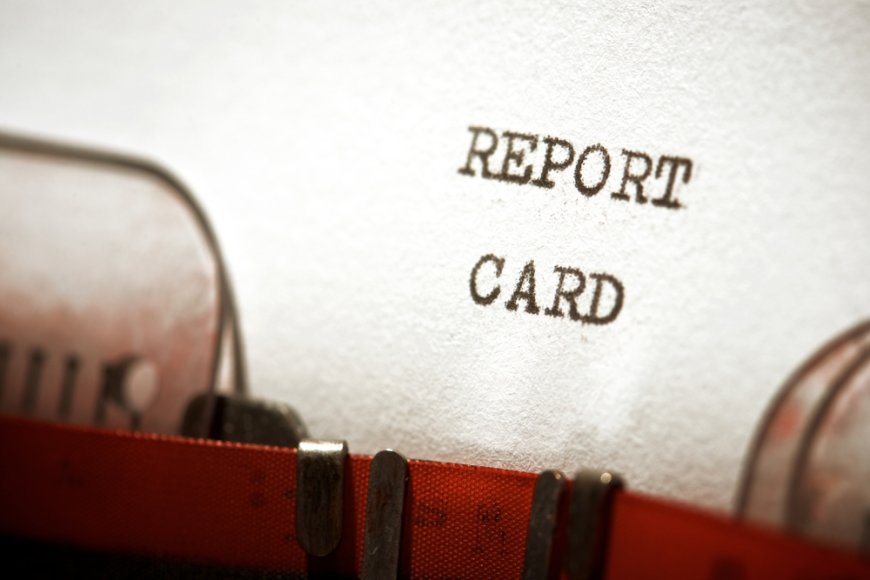


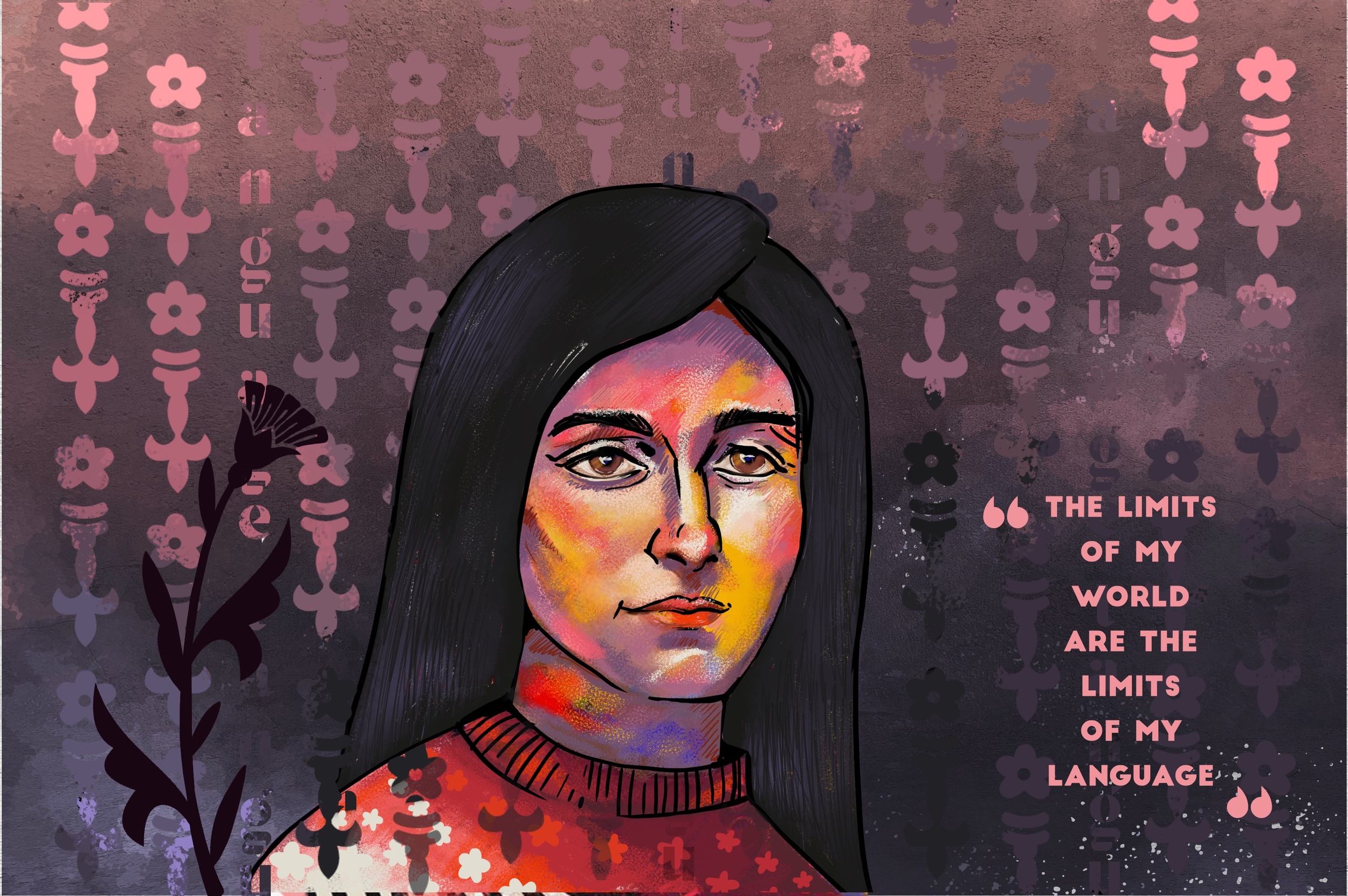



Comments