বোয়াস মন-ভাষা সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে এক ধরনের দ্বিধায় ছিলেন। জাতিসমূহের পার্থক্য নিয়ে ১৯শ শতাব্দীর আলোচনাগুলো প্রায়ই মানবজাতির এক অনুমিত শ্রেণিবিন্যাসের ওপর ভিত্তি করত। ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো যে, বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছেছে – এবং এটি তাদের জ্ঞানগত ক্ষমতার পার্থক্যের ফল। এই শ্রেণিবিন্যাসের শীর্ষে ছিল ১৯শ শতাব্দীর ইউরোপীয় মানুষ, যিনি সবদিকে তার মানসিক ক্ষমতা প্রসারিত করেছেন; আর নীচে ছিল বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যাদের সাধারণত মনে করা হতো মানবতার চিরন্তন শৈশবে আটকে আছে অথবা "সভ্যতা"-র এক পূর্বাবস্থার অবক্ষয়ে পতিত হয়েছে।
মনোভাবগুলো ছিল না একরূপ: এই সময়ে মানব সমাজ, সংস্কৃতি ও জ্ঞানগত বিবর্তনের বহু ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল, যেখানে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্যকে স্বীকার করা হতো। কিন্তু হামবোল্ট, স্টেইনথাল এবং গাবেলেনৎসের মতো ব্যক্তিত্বরা, যারা মানব বৈচিত্র্যে আনন্দ পেতেন এবং প্রতিটি ভাষার স্বকীয়তাকে প্রশংসা করতেন, তারাও কিছু ভাষাকে অন্য ভাষার তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিতেন। স্টেইনথাল যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আমেরিকান ভাষাগুলোর আসলে কোনো অভ্যন্তরীণ রূপ নেই। তাদের ব্যাকরণে নিঃসন্দেহে জটিল নির্মাণ পাওয়া গেলেও, সেগুলো কেবল কংক্রিট ধারণার মিশ্রণমাত্র, কোনো অন্তর্নিহিত আনুষ্ঠানিক কাঠামো নেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নৃতত্ত্ববিদ এবং ভাষাবিদদের মধ্যে তৎকালীন মনোভাব ছিল আরও চরমপন্থী।
নৃতত্ত্ববিদরা ভাষা ও মনের মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগ নিয়ে চিন্তাভাবনা চালিয়ে গিয়েছিলেন
বোয়াস এ ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে অবস্থান নেন। তিনি আসলে তার বিরোধীদের সাথে একমত হয়েছিলেন যে, আদিবাসী ভাষাগুলোতে কিছু কথিত ঘাটতি রয়েছে, তবে তিনি একে মানসিক বিকাশের সূচক হিসেবে স্বীকার করেননি। অনেক আমেরিকান ভাষায় বিমূর্ত শব্দ এবং অসীম সংখ্যার শব্দ নেই – এটি তিনি স্বীকার করেছিলেন – তবে এর কারণ এই নয় যে তাদের বক্তারা এমন ধারণা বোঝার অক্ষম। বরং কারণ হলো, তাদের কখনো বিমূর্ত ধারণায় কথা বলার বা উচ্চ সংখ্যা গণনা করার প্রয়োজন হয়নি, তাই তারা তাদের ভাষায় এমন রূপ তৈরি করার সুযোগ পায়নি। যদি এ ধরনের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়, তবে তাদের ভাষা দ্রুত মানিয়ে নেবে।
বোয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে গঠিত হয়েছিল তার বার্লিনের সাবেক পরামর্শদাতা নৃতাত্ত্বিক অ্যাডলফ বাস্তিয়ান (১৮২৬-১৯০৫)-এর শিক্ষায়। বাস্তিয়ান মানবজাতির "মানসিক ঐক্য" নীতিকে সমর্থন করেছিলেন – ধারণাটি হলো, সকল মানুষ, তাদের বংশ বা বর্তমান সাংস্কৃতিক অবস্থা যাই হোক না কেন, মূলত একই মানসিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর তথাকথিত ভিন্ন "জাতিগত চিন্তা" আসলে মানবজাতির সাধারণ "প্রাথমিক চিন্তার" ভিন্ন বিন্যাসমাত্র। মানুষের মন সর্বত্র মূলত একই।
আমরা তাই দেখি যে ১৯শ শতাব্দীতে ভাষাগত আপেক্ষিকতা নিয়ে একাডেমিক মনোভাবের একটি স্পষ্ট বাঁক তৈরি হয়। শতাব্দীর শুরুতে, হের্ডার এবং হামবোল্টের মতো ব্যক্তিত্বদের লেখনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভাষাগত আপেক্ষিকতা ছিল ভাষা অধ্যয়নে এক সম্মানজনক অবস্থান। কিন্তু শতাব্দীর অগ্রগতির সাথে সাথে একাডেমিক ভাষাতত্ত্ব ক্রমশ তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাকরণবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে, যাদের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কারিগরি এবং প্রমাণনির্ভর। এই বৌদ্ধিক পরিবেশে, ভাষাবিদেরা ধীরে ধীরে ভাষার অন্তর্নিহিত ধারণাগত কাঠামো নিয়ে আলোচনার মতো অস্পষ্ট প্রশ্ন থেকে সরে আসতে থাকেন। অপরদিকে, নৃতত্ত্ববিদেরা পুরো ১৯শ শতাব্দী জুড়েই ভাষা ও মনের মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগ বিবেচনা করতে থাকেন। তবে তাদের আলোচনার শ্রেণিবদ্ধ কাঠামো শতাব্দীর শেষে সমালোচনার মুখে পড়ে, যেখানে নেতৃত্ব দেন বোয়াস।
পরবর্তী সময়ে প্রচলিত "স্যাপির-ওরফ অনুমান" অনেক দিক থেকেই ১৯শ শতাব্দীর বিতর্কেরই ধারাবাহিকতা। এডওয়ার্ড স্যাপির (১৮৮৪-১৯৩৯) এবং তার ছাত্র বেঞ্জামিন লি ওরফ (১৮৯৭-১৯৪১) হামবোল্টীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। স্যাপির জার্মান ভাষাতত্ত্বে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন: তার মাস্টার্স থিসিস ছিল হের্ডারের Treatise on the Origin of Language-এর ওপর। তিনি বোয়াসের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং নিবেদিত ছাত্রদের একজন ছিলেন এবং তার শিক্ষকের অবস্থানকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিলেন। স্যাপির ১৯২১ সালে লিখেছিলেন: "ভাষা ও আমাদের চিন্তার ধারা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত – এক অর্থে তারা একই জিনিস।" তবে বোয়াসের মতো তিনিও জোর দিয়েছিলেন যে, মানুষের প্রজাতির মধ্যে চিন্তার কোনো "গুরুত্বপূর্ণ জাতিগত পার্থক্য" নেই, এবং সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। তাই ভাষার গঠন থেকে কথিত বিবর্তনীয় ধাপ অনুমান করা অসম্ভব: "ভাষাগত রূপের ক্ষেত্রে, প্লেটো হাঁটছে ম্যাসিডোনিয়ার শূকর পালকের সাথে, কনফুসিয়াস হাঁটছে আসামের শিরশিকারী বর্বরের সাথে।"
অতীতের পক্ষপাতদুষ্ট গবেষণা থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও, স্যাপির এখনও বিশ্বের ভাষাগুলোর ব্যাকরণিক "প্রক্রিয়া" এবং "ধারণা" বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, যাতে প্রতিটি ভাষার "ধরন বা পরিকল্পনা বা গঠনমূলক প্রতিভা" চিহ্নিত করা যায়। তবে এই প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল ভাষাগত রূপের অন্তত আংশিক স্বায়ত্তশাসনের বিশ্বাস দ্বারা। স্যাপির মতে, প্রতিটি ভাষার একটি "অভ্যন্তরীণ ধ্বনিতন্ত্র" এবং "ব্যাকরণিক রূপায়ণের স্তরে নির্দিষ্ট বিন্যাসের অনুভূতি" থাকে, যা নিজস্বভাবে কাজ করে, নির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করার প্রয়োজন হোক বা নির্দিষ্ট ধারণার সমষ্টিকে বাহ্যিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজন হোক না কেন। মনে হয় ভাষা পুরোপুরি সেই চিন্তার ধারা দ্বারা বন্দি নয়।
ভাষাগত রূপকে আংশিকভাবে স্বতন্ত্র হিসেবে ধরা হয়েছিল ১৯শ শতাব্দীর তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাকরণবিদদের ধ্বনিগত আইন সংক্রান্ত ধারণাতেও। ২০শ শতাব্দীতে অনেক ভাষাবিদ সরাসরি ভাষার গঠনকে তাদের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে আলাদা করে ফেলেছিলেন, এমন একটি বস্তু হিসেবে যা তারা জ্ঞান বা বক্তৃতার শারীরিক উৎপাদন ও গ্রহণের বিস্তৃত প্রশ্ন থেকে স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারতেন। এ সময় জেনেভার ভাষাবিদ ফের্দিনান দে সসুর (১৮৫৭-১৯১৩) la langue (ভাষা) এবং la parole (বক্তৃতা)-এর মধ্যে একটি পার্থক্য প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তী ভাষাতত্ত্বে মৌলিক হয়ে ওঠে। La langue হলো প্রতিটি ভাষার বিমূর্ত, স্বনির্ভর ব্যবস্থা, আর la parole হলো la langue ব্যবহার করে বাস্তব উচ্চারণ তৈরি করা। সসুর যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ভাষাবিদদের উচিত প্রতিটি langue-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা, এটি বক্তাদের মনের ও মুখের ভেতরে কীভাবে কাজ করছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে। এগুলো মনোবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা ও পদার্থবিজ্ঞানের মতো প্রতিবেশী বিজ্ঞানের কাজ। ভাষার আনুষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে স্যাপিরের অবস্থানকে এই প্রবণতার অংশ হিসেবে বোঝা যায়, যদিও একইসাথে তিনি স্পষ্টভাবে তার হামবোল্টীয় ঐতিহ্য পুরোপুরি ত্যাগ করতে চাননি, যার মধ্যে ছিল মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক উদ্বেগ।
ভাষার যাদু ভাঙার, এর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এক আকাঙ্ক্ষা ছিল
কিন্তু তথাকথিত স্যাপির-ওরফ অনুমানের ভাষাগত নিয়তিবাদ সম্পর্কে কী বলা যায়? যদিও স্যাপির বা ওরফ কেউই কখনো ভাষার চিন্তার ওপর প্রভাব সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট, পরীক্ষাযোগ্য প্রস্তাব দেননি, তবুও তারা নিঃসন্দেহে এমন প্রভাব কল্পনা করেছিলেন। ১৯২৯ সালে স্যাপির লিখেছিলেন:
“আসল বিষয়টি হলো, ‘বাস্তব জগৎ’ বড় অংশে আমাদের ভাষাগত অভ্যাস দ্বারা অচেতনভাবে গড়ে ওঠে... বিভিন্ন সমাজ যে জগতগুলোতে বাস করে, সেগুলো পৃথক জগত – কেবল একই জগত নয়, যার ওপর ভিন্ন ভিন্ন লেবেল লাগানো হয়েছে... আমরা যেমন দেখি, শুনি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তার বড় অংশই ঘটে কারণ আমাদের সমাজের ভাষাগত অভ্যাস আমাদের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ধারা বেছে নিতে প্রণোদিত করে।”
স্যাপির ও ওরফের বক্তব্য প্রতিফলিত করেছিল সমসাময়িক এক নৈতিক আতঙ্ককে – ভাষার ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ে। ২০শ শতাব্দীর শুরুতে নতুন প্রযুক্তি যেমন রেডিও ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নতুন ধরণের প্রচারণা ছড়িয়ে পড়েছিল, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়কর অস্থিরতা এবং ইউরোপ জুড়ে স্বৈরশাসক সরকারগুলোর উত্থানকে সহায়তা করেছিল। ভাষার যাদু ভাঙার, এর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার, এটিকে অযৌক্তিকতা ও বর্বরতার সমর্থক থেকে মুক্ত করে প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তার দাসে রূপান্তর করার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন এই সময়ে উদীয়মান বিশ্লেষণমূলক দর্শনের ভাষাগত মোড়ে। জনপ্রিয় স্তরে অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল ভাষার অর্থ নিয়ে, যেমন সি.কে. ওগডেন ও আই.এ. রিচার্ডসের The Meaning of Meaning (১৯২৩), আলফ্রেড কোরজিবস্কির Science and Sanity (১৯৩৩), এবং স্টুয়ার্ট চেজের The Tyranny of Words (১৯৩৮)। এটাই সেই জগৎ, যেখানে অরওয়েলের "নিউজপিক"-এ ভাষা মনের প্রভু হয়ে ওঠে।
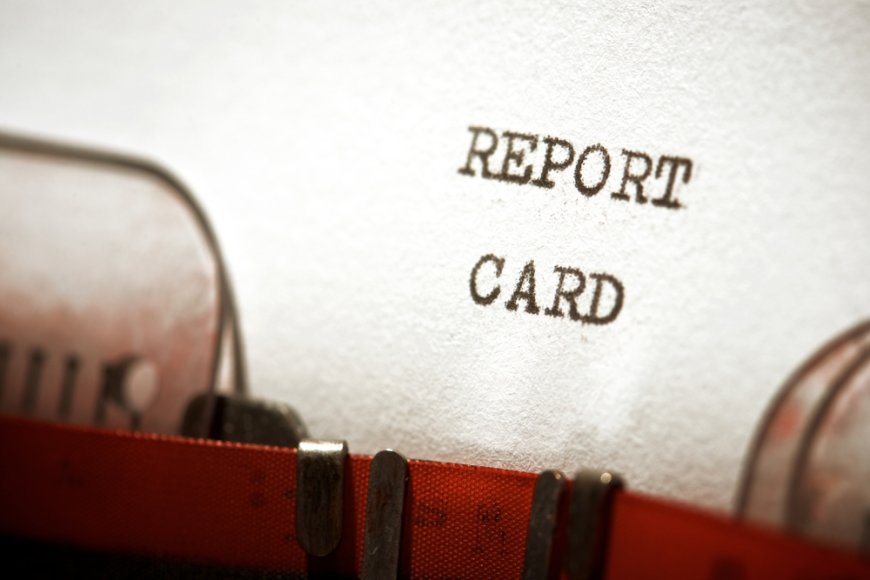


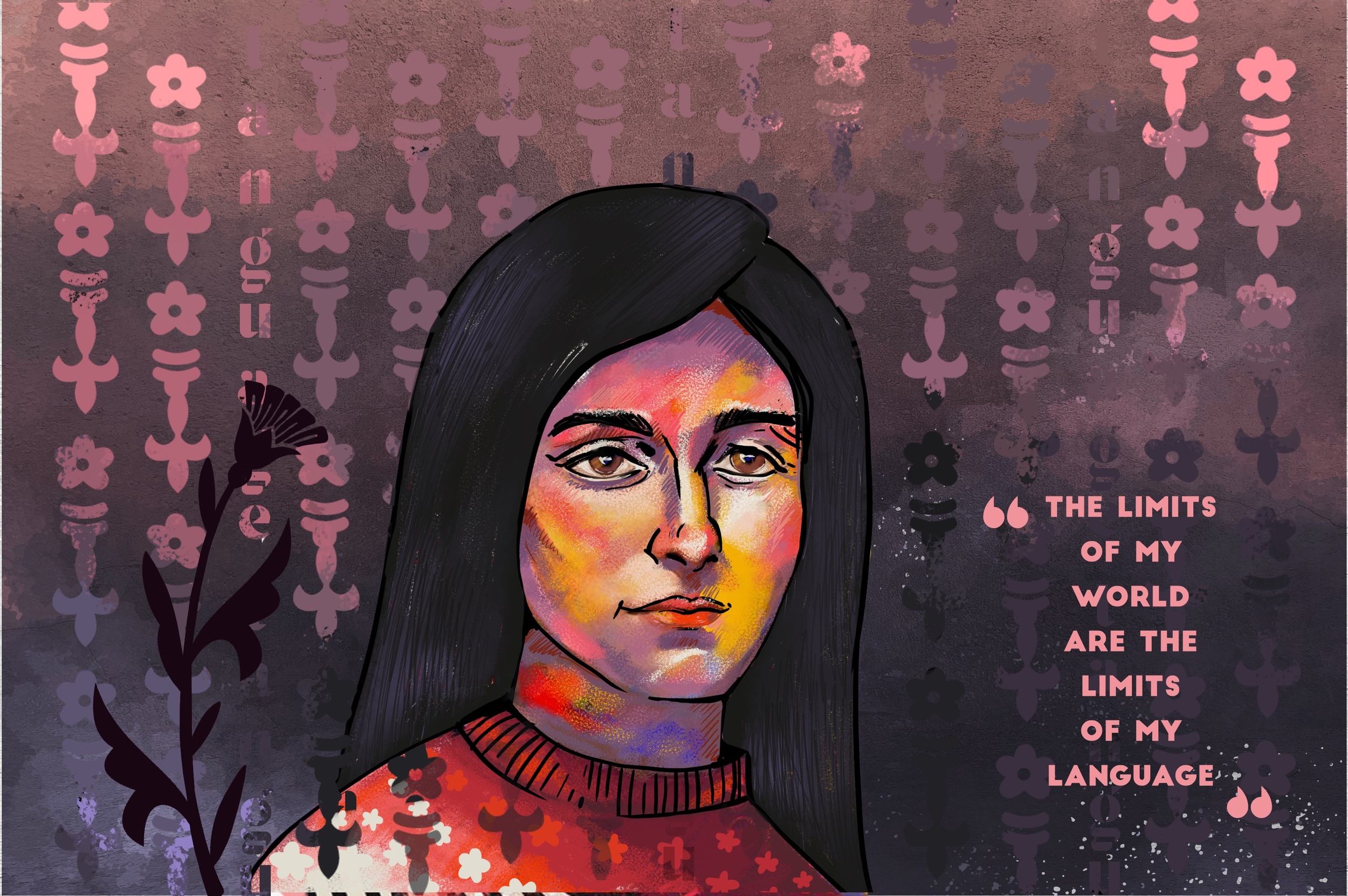


Comments