সক্রেটিস: এথেন্সের রহস্যময় গ্যাডফ্লাই
সক্রেটিস, এথেন্সের দার্শনিক যিনি আনুমানিক ৪৬৯ থেকে ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, চিন্তার ইতিহাসে অন্যতম রহস্যময় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত। তাঁর পূর্বসূরি প্রাক-সক্রেটিসীয় দার্শনিকরা যেখানে পরমাণু, মৌল বা অস্তিত্বের প্রবাহ নিয়ে মহাজাগতিক অনুমান করতেন, সক্রেটিস সেদিকে না গিয়ে মনোযোগ দেন মানুষের আত্মা, নীতি ও প্রশ্ন করার শিল্পে। তাঁর জীবন ও ভাবনা তিনি নিজে কোনো রচনায় রেখে যাননি; বরং সমসাময়িক নাট্যকার, ইতিহাসবিদ ও শিষ্যদের বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। তাঁর অনুসন্ধানের পদ্ধতি—যা এলেনখাস বা দ্বন্দ্বাত্মক আলোচনার নামে পরিচিত—এথেন্স সমাজের ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। এই বিশ্লেষণে সক্রেটিসের জীবনী, দর্শনপদ্ধতি, মূল মতবাদ, বিচার ও মৃত্যু এবং উত্তরাধিকারের আলোকে আমরা তাঁর চিন্তার রূপরেখা খুঁজব, যেখানে যুক্তিবোধের মাধ্যমে নৈতিকতার প্রতিশ্রুতি মিশে গেছে মানবিক আবেগের অযৌক্তিকতায়, আর প্রজ্ঞার অনুসন্ধান শেষ হয়েছে হেমলকের পাত্রে।
ঐতিহাসিক সক্রেটিসকে পুনর্গঠন
সক্রেটিসকে বোঝার মূল চ্যালেঞ্জ তাঁর জীবনের নির্ভরযোগ্য উৎসের অভাব। তাঁর কোনো রচনা অবশিষ্ট নেই। ফলে আমরা চারটি প্রধান সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি—রসিক নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিস, ইতিহাসবিদ জেনোফন, দার্শনিক প্লেটো এবং সংক্ষিপ্তভাবে অ্যারিস্টটল। প্রত্যেকেই ভিন্ন রূপে তাঁকে চিত্রিত করেছেন, ফলে সরল জীবনী রচনা কঠিন হয়ে পড়ে।
অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর নাটক দ্য ক্লাউডস (৪২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-এ সক্রেটিসকে এক ভণ্ড, নাস্তিক এবং কূটকৌশলী হিসেবে বিদ্রূপ করেছেন—যিনি ঝুলন্ত ঝুড়িতে বসে আকাশের রহস্য ভাবছেন আর প্রথাগত ধর্মকে উপহাস করছেন। যুদ্ধকালীন আতঙ্কের প্রেক্ষাপটে রচিত এই ব্যঙ্গচিত্রে সক্রেটিসকে বিপজ্জনক উদ্ভাবক হিসেবে দেখানো হয়। অন্যদিকে, বাস্তববাদী সেনাপতি ও সক্রেটিসের সহচর জেনোফন তাঁর মেমোরাবিলিয়া ও সিম্পোজিয়াম-এ সক্রেটিসকে ধার্মিক, সংযমী নীতিবাদী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন—একজন বুদ্ধিদীপ্ত চাচার মতো, যিনি গৃহস্থালি অর্থনীতি, বন্ধুত্ব ও নাগরিক দায়িত্ব নিয়ে আলাপ করেন।
প্লেটো, তাঁর সর্বাধিক খ্যাতিমান শিষ্য, সংলাপসমূহে সক্রেটিসকে আদর্শায়িত করেছেন। অ্যাপলজি থেকে ফাইডো পর্যন্ত এই রচনাগুলোয় সক্রেটিস হয়ে উঠেছেন ন্যায়, জ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের মুখপাত্র। তবে অনেক সময় প্লেটোর নিজস্ব দর্শনের ছাপও স্পষ্ট। অ্যারিস্টটল, পরবর্তী প্রজন্মে লিখে, সক্রেটিসকে আরও বিশ্লেষণাত্মকভাবে দেখান—তাঁর অবদানকে নৈতিক সংজ্ঞা ও আব inductive পদ্ধতিতে সীমিত রেখে প্লেটোর আধ্যাত্মিকতার থেকে আলাদা করেন।
এসব মেলালে যে সক্রেটিসের চিত্র পাওয়া যায় তা হলো: সোফ্রোনিস্কাস নামের এক পাথরশিল্পীর ও ফ্যানারেট নামের ধাত্রী-নারীর সন্তান। শারীরিকভাবে তেমন আকর্ষণীয় ছিলেন না—খাটো, মোটা, চ্যাপ্টা নাক, উঁচু চোখ, স্যাটায়ারের মতো মুখ। তবু ছিল অদ্ভুত এক আকর্ষণ ও সহনশীলতা। তিনি শানথিপ্পে নামের এক খ্যাত কটুস্বভাবী স্ত্রীকে বিয়ে করেন ও তিন পুত্রের জনক হন। সেনাবাহিনীতে হপ্লাইট হিসেবে লড়াই করেছেন পোটিডাইয়া, ডেলিয়াম ও অ্যামফিপোলিসে; যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাহসিকতা ও ধৈর্য নজর কেড়েছে।
রাজনীতিতে সক্রেটিস ছিলেন গণতন্ত্রের সমালোচক। যদিও তিনি পরিষদে ভোট দিয়েছেন, ৫০০ সদস্যের কাউন্সিলে দায়িত্ব পালন করেছেন, তবু ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বে ৩০ জন স্বৈরশাসকের অন্যায় আদেশ অমান্য করেছেন। তাঁর বন্ধু ক্রিটিয়াস ও আলসিবিয়াদেসের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁকে সন্দেহভাজন করে তোলে। সোনালি যুগের এথেন্স তখন ভেঙে পড়ছিল যুদ্ধ, মহামারী ও সাম্রাজ্যবাদী লোভে। সক্রেটিস ন্যাড়া পায়ে, এলোমেলো চাদর জড়িয়ে আগোরায় ঘুরতেন, সবার সাথে প্রশ্ন করতেন: “নিজেকে জানো”—ডেলফির এই মন্ত্রকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এই সৈনিক, গ্যাডফ্লাই ও ধাত্রীর ছেলে হয়ে ওঠেন এমন এক দার্শনিক, যাঁর দর্শন কোনো সুসংহত ব্যবস্থা নয় বরং এক চর্চা—সংলাপের মাধ্যমে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।
সক্রেটিসীয় পদ্ধতি: দ্বন্দ্ব ও মানসিক ধাত্রীবিদ্যা
সক্রেটিসের দর্শনের প্রকৃত প্রাণশক্তি নিহিত ছিল এলেনখাস-এ—প্রশ্নোত্তর, খণ্ডন ও বিশ্লেষণের এমন এক কৌশল যা ধীরে ধীরে আলাপচারিতার ভেতর থেকে বিরোধ ও অজ্ঞতাকে উন্মোচিত করত। তিনি এই প্রক্রিয়াকে তুলনা করেছিলেন তাঁর মায়ের পেশার সঙ্গে—ধাত্রীবিদ্যা বা মায়েউটিক্স-এর সাথে। যেমন একজন ধাত্রী মায়ের গর্ভে থাকা শিশুর জন্মে সহায়তা করে, তেমনি সক্রেটিস তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তা ও বিশ্বাসকে “প্রসব” করাতেন। তিনি নিজে কিছু জ্ঞান চাপিয়ে দিতেন না, বরং আলাপচারিতার মাধ্যমে অপরকে নিজের ভেতরেই লুকিয়ে থাকা সত্য উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করতেন।
ডেলফির অরাকল একবার ঘোষণা করেছিল যে সক্রেটিসই জীবিতদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। সক্রেটিস এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি নিজেকে কখনোই জ্ঞানী মনে করতেন না। বহু চিন্তাভাবনার পর তিনি একে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে—“প্রকৃত জ্ঞান আসলে নিহিত আছে এই উপলব্ধিতে যে, আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না।” এই উপলব্ধিই তাঁকে এক অদম্য অনুসন্ধানী করে তুলেছিল।
এরপর তিনি এথেন্সের রাজনীতিবিদ, কবি, কারিগর—যাদের সমাজে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো—তাদের কাছে যেতেন এবং ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করতেন। প্রায়ই দেখা যেত, যাদেরকে শহর অত্যন্ত প্রাজ্ঞ মনে করত, তারা নিজেদের বক্তব্য টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন। যেমন তিনি অ্যাপলজি-তে উল্লেখ করেন:
“যাকে জ্ঞানী বলা হয়, তার সঙ্গে কথা বললাম… কিন্তু আলাপের পর দেখলাম, সে যতটা মনে হয় ততটা জ্ঞানী নয়।”
এই প্রক্রিয়াটি অনেক সময় ছিল গভীরভাবে অস্বস্তিকর। কারণ, যে কোনো মানুষ স্বাভাবিকভাবে চায় নিজের জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিতে। অথচ সক্রেটিস তাঁদের ভেতরের অসঙ্গতি প্রকাশ করে দিতেন। এর ফলে অনেকেই বিরক্ত ও বিব্রত হতো। আবার অন্যদিকে, যারা এই ধাক্কা সহ্য করতে পারত, তাদের জন্য এই আলোচনাগুলো হয়ে উঠত আত্ম-উপলব্ধির এক মহামূল্যবান সুযোগ।
ফলে, সক্রেটিসীয় পদ্ধতি ছিল দ্বিমুখী—একদিকে গণতান্ত্রিক, কারণ যে কেউ এর অংশ নিতে পারত; আবার অন্যদিকে ছিল অভিজাত, কারণ কেবলমাত্র যারা মানসিকভাবে শক্ত ও আত্মসমালোচনায় প্রস্তুত, তারাই এই আলোচনার প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এতে তিনি সমাজের সাধারণ মানুষকে যেমন নাড়া দিয়েছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও অস্বস্তির কারণ হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি এথেন্সের শক্তিশালী গোষ্ঠীর কাছে এক বিপজ্জনক ও বিরক্তিকর “গ্যাডফ্লাই”-এ পরিণত হন।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/ri8xzxrae.jpg'>
সক্রেটিস বারবার মনে করিয়ে দিতেন, জীবনের প্রকৃত মূল্য নিহিত আছে পরীক্ষার ভেতরেই। তাঁর বিখ্যাত উক্তি—“অপরীক্ষিত জীবন বেঁচে থাকার যোগ্য নয়”—শুধু একটি দার্শনিক নীতি নয়, বরং মানবজীবনের এক গভীর আহ্বান। তাঁর এই প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি দর্শনকে মহাজাগতিক জল্পনা থেকে ফিরিয়ে এনেছিল সরাসরি মানুষের জীবনে, যেখানে ন্যায়, গুণ, পাপ ও জ্ঞানের মতো বিষয়গুলো নিয়ে সরল অথচ গভীর আলোচনা সম্ভব হয়।
নৈতিক মতবাদ: জ্ঞানই গুণ
সক্রেটিস নৈতিক দর্শনের জগতে এক মৌলিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের সব অনৈতিক আচরণ বা অন্যায় মূলত অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ, কেউ কখনো সচেতনভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ কাজ করে না। মানুষ যখন ভুল করে, তখন আসলে সে নিজের প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়। সে ভেবে নেয় যে, কোনো তাৎক্ষণিক আনন্দ বা ক্ষুদ্র লাভ তার জন্য ভালো—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটিই তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এই চিন্তাভাবনা থেকে সক্রেটিস এক মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন: জ্ঞানই প্রকৃত গুণ (virtue is knowledge)। ন্যায় (justice), সাহস (courage), সংযম (temperance) কিংবা ধার্মিকতা (piety)—সব গুণই আসলে এককেন্দ্রিক, এবং তা হচ্ছে জ্ঞানের বহুমাত্রিক রূপ। যে সত্যিকারের জানে কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর, সে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পথে হাঁটবে না। সুতরাং, নৈতিকতা শেখানো যায় এবং শেখানো উচিত—যেমনভাবে গণিত বা জ্যামিতি শেখানো সম্ভব।
সক্রেটিস মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ হিসেবে আত্মাকেই গুরুত্ব দিতেন। তাঁর দৃষ্টিতে আত্মা অমর, ঈশ্বরীয় এবং জ্ঞানের আধার; আর দেহ হলো কেবল এক অস্থায়ী আবরণ, কখনো কখনো এক “কারাগার”। তিনি বিশ্বাস করতেন, আত্মার যত্ন নেওয়া ও তাকে সৎ পথে পরিচালিত করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। এই কারণে তিনি সবসময় প্রশ্ন করতেন: “তুমি কীভাবে জীবন যাপন করছ? তোমার আত্মাকে কীভাবে পরিচর্যা করছ?”—কারণ তাঁর মতে, মানুষের সত্যিকারের পরিচয় আত্মায় নিহিত। যদিও সক্রেটিস মৃত্যুর পর আত্মার ভাগ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করেননি, তবে তাঁর শেষ সময়ের কথোপকথনে (বিশেষত ফাইডো সংলাপে) আত্মার অমরত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, দর্শনের চর্চাই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং মৃত্যুর পর আত্মাকে উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছে দেয়।
তবে সক্রেটিসের এই “জ্ঞানই গুণ” মতবাদ পরে সমালোচনার মুখে পড়ে। অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়েছিলেন, অনেক সময় মানুষ সঠিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ভুল কাজ করে—যা আক্রাসিয়া বা দুর্বল ইচ্ছাশক্তির পরিচায়ক। উদাহরণস্বরূপ, একজন মানুষ জানেন অতিভোজন ক্ষতিকর, কিন্তু ক্ষণিকের আনন্দে তিনি অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ফেলেন। এর মানে হলো, জ্ঞান থাকলেও বাস্তবে মানুষ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না। তবুও সক্রেটিসের অবস্থান গভীর এক আশাবাদের বহিঃপ্রকাশ। তিনি মানুষের প্রকৃতিকে যুক্তিনির্ভর ধরে নিয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন, যদি মানুষ সত্যিকার অর্থে জানে কোনটি কল্যাণকর, তবে সে কখনো ভুল পথে যাবে না। এভাবেই তিনি নৈতিকতাকে এক ধরণের বিজ্ঞান হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যা যুক্তি ও জ্ঞানের মাধ্যমে শেখা ও আয়ত্ত করা যায়।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/aosbbk2c5.jpg'>
বিচার ও মৃত্যু: দর্শনের ট্রায়াল
৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বের এথেন্স। গণতন্ত্র সদ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত এক নগররাষ্ট্র। সেই সময়ে এক বৃদ্ধ দার্শনিককে ডাকা হলো আদালতে। নাম তাঁর সক্রেটিস। অভিযোগ—যুবকদের বিপথগামী করা, আর দেবতাদের অস্বীকার করে নতুন দেবতা প্রচার। আসলে এর পেছনে ছিল এক দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রতিশোধ, কারণ সক্রেটিস বছরের পর বছর ধরে এথেন্সের ক্ষমতাধরদের অজ্ঞতা প্রকাশ্যে নগ্ন করে দিয়েছেন তাঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্নোত্তরে।
আদালত ভরপুর—৫০১ জন জুরি, দর্শক, শিষ্য ও কৌতূহলী নাগরিক। সক্রেটিস দাঁড়ালেন আসামির আসনে, কিন্তু তাঁর ভঙ্গি ছিল অনড়। অ্যাপলজি-তে যেভাবে তিনি বলেছিলেন, সেভাবেই আজও ঘোষণা করলেন: “আমি এথেন্সের আত্মার জন্য সেই গ্যাডফ্লাই, যে নগরটিকে জাগিয়ে রাখে।” তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কৌতুক করলেন—“আমার কাজের জন্য শাস্তি নয়, বরং রাষ্ট্র যেন প্রতিদিন আমাকে প্রাইতানিয়নে ভোজন করায়।” কথাটি শুনে আদালতে ফিসফিস, কেউ হাসল, কিন্তু জুরিদের চোখে জমল রাগের আগুন।
অবশেষে ভোট হলো। সামান্য ব্যবধানে দোষী সাব্যস্ত হলেন সক্রেটিস। যখন শাস্তি নির্ধারণের পালা এল, তখন তাঁর সামনে ছিল দুই রাস্তা—মৃত্যুদণ্ড কিংবা স্বেচ্ছাপ্রস্তাবিত শাস্তি। সক্রেটিস বিন্দুমাত্র ভীত নন। জুরিরা ঘোষণা করল: বিষপান করে মৃত্যুদণ্ড।
তাঁর বন্ধু ক্রিটো গোপনে প্রস্তাব দিলেন—“গুরু, পালিয়ে যান, আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি।” সক্রেটিস শান্তভাবে উত্তর দিলেন: “আইন আমাদের পিতামাতার মতো; আমি যদি আইন ভাঙি, তবে গোটা নগর ধ্বংস হবে। ন্যায় মানা আমার জীবনের শপথ—এখন যদি তা ভঙ্গ করি, তবে এতদিনের জীবন বৃথা।”
শেষ দিনটি এলো। সক্রেটিস কারাগারে শিষ্যদের সঙ্গে বসে আত্মার অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন: “দার্শনিকের জীবন আসলে মৃত্যুর প্রস্তুতি।” তাঁর কণ্ঠ দৃঢ়, চোখে কোনো ভয় নেই—শুধু সত্য খোঁজার অদম্য আগ্রহ।
অবশেষে সৈনিক হেমলক নিয়ে এলো। সক্রেটিস বিষের পেয়ালা হাতে তুলে নিলেন, শান্তভাবে পান করলেন। শিষ্যরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, কিন্তু তিনি অবিচল। শেষ মুহূর্তে ক্রিটোকে বললেন:
“ক্রিটো, আমরা আসক্লেপিয়াসকে একটি মোরগ ধার করি—ভুলো না, তা শোধ করে দিও।”
দেহ নিস্তব্ধ হলো, আত্মা যেন মুক্তির ডানা মেলল। আর এভাবেই সক্রেটিস মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরজীবী হয়ে উঠলেন—দর্শনের প্রথম শহীদ, যিনি প্রমাণ করলেন যে সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া সম্ভব।
উত্তরাধিকার: প্লেটো ও তার পর
সক্রেটিস দর্শনের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে গ্রিক চিন্তাবিদরা মূলত মহাবিশ্বের গঠন, পদার্থের আদি উপাদান বা প্রকৃতির রহস্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন—থেলেস, হেরাক্লিটাস বা ডেমোক্রিটাস সবাই প্রকৃতির উপাদান বা মহাজাগতিক নিয়ম অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেছিলেন। সক্রেটিস এই ধারা ভেঙে মানুষকে ফিরিয়ে আনলেন মানুষের মধ্যেই। তিনি প্রশ্ন তুললেন—“ন্যায় কী?”, “সাহস কী?”, “সৎ জীবন কীভাবে যাপন করা যায়?”। এভাবেই দর্শন প্রকৃতি থেকে নৈতিকতায়, মহাবিশ্ব থেকে মানবজীবনে সরে আসে।
তাঁর এই বুদ্ধিবিপ্লবের উত্তরাধিকার বহন করেন শিষ্যরা।
প্লেটো, যিনি সক্রেটিসের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই শোক ও অনুপ্রেরণাকে রূপ দিলেন দার্শনিক সংলাপে। প্লেটোর রচনাতেই সক্রেটিসের কণ্ঠ আজও জীবন্ত—যেখানে শিক্ষক আর শিষ্যের সংলাপে নৈতিকতা, রাজনীতি ও জ্ঞানের গভীর প্রশ্ন আলোচিত হয়। সক্রেটিসের অবিনশ্বর প্রভাবেই প্লেটো দর্শনকে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামোয় পরিণত করেন, যা আজও পশ্চিমা চিন্তার ভিত্তি।
অন্য শিষ্য জেনোফন সক্রেটিসের ভাবনাকে ছড়িয়ে দেন আরও বাস্তব ও নৈতিক ব্যবহারে। তাঁর লেখায় সক্রেটিসকে দেখা যায় নিত্যজীবনের উপদেশদাতা হিসেবে—কৃষক, সৈনিক বা গৃহস্থকে কীভাবে সৎভাবে বাঁচতে হয়, তা বোঝাতে।
এরপর আসেন অ্যারিস্টটল—প্লেটোর শিষ্য, কিন্তু স্বতন্ত্র চিন্তার অধিকারী। তিনি সক্রেটিসের যুক্তি ও বিশ্লেষণকে আরও বৈজ্ঞানিক রূপ দেন। নৈতিকতার আলোচনাকে তিনি গোল্ডেন মিন—অর্থাৎ অতিরিক্ততা আর অভাবের মাঝামাঝি অবস্থান—এর তত্ত্বে পরিণত করেন। এই ধারা পরবর্তী পশ্চিমা নৈতিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করে।
তবে সক্রেটিসের প্রভাব এখানেই থেমে থাকেনি।
স্টোয়িক দর্শন তাঁকে দেখা যায় এক আদর্শ হিসেবে—যিনি নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কষ্টকে সহ্য করেন এবং সত্যের প্রতি অনড় থাকেন।
আলোকায়ন যুগের দার্শনিকেরা সক্রেটিসকে দেখেছিলেন যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার প্রতীক হিসেবে, যিনি অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করে নতুন আলো আনেন। এমনকি আধুনিক গণতন্ত্রের সমালোচনার ক্ষেত্রেও সক্রেটিস এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি দেখিয়েছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সবসময় ন্যায়সঙ্গত নয়—কারণ তাঁর নিজের মৃত্যুদণ্ডই ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফল।
তবুও সক্রেটিসের প্রতি সমালোচনা কম নয়। তিনি আবেগ বা মানবিক অনুভূতির গুরুত্বকে তুলনামূলকভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর সময়ের সামাজিক অবিচার—যেমন দাসপ্রথা কিংবা নারীর অধিকারহীনতা—তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেননি। ফলে তাঁকে অনেকেই মনে করেন এক সীমাবদ্ধ যুগের সন্তান।
তবুও সক্রেটিস আজও টিকে আছেন এক অনন্য প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে। তিনি বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মানুষকে নিজের অজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, আবার সত্যের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর অমর উক্তি—“আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না”—মানুষকে শেখায় বিনয়, আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানের অন্তহীন অনুসন্ধান।
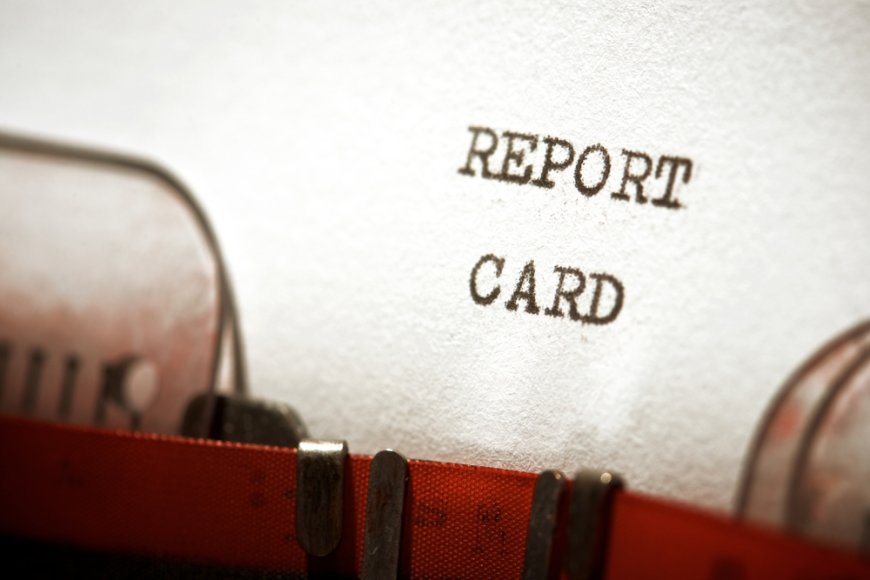


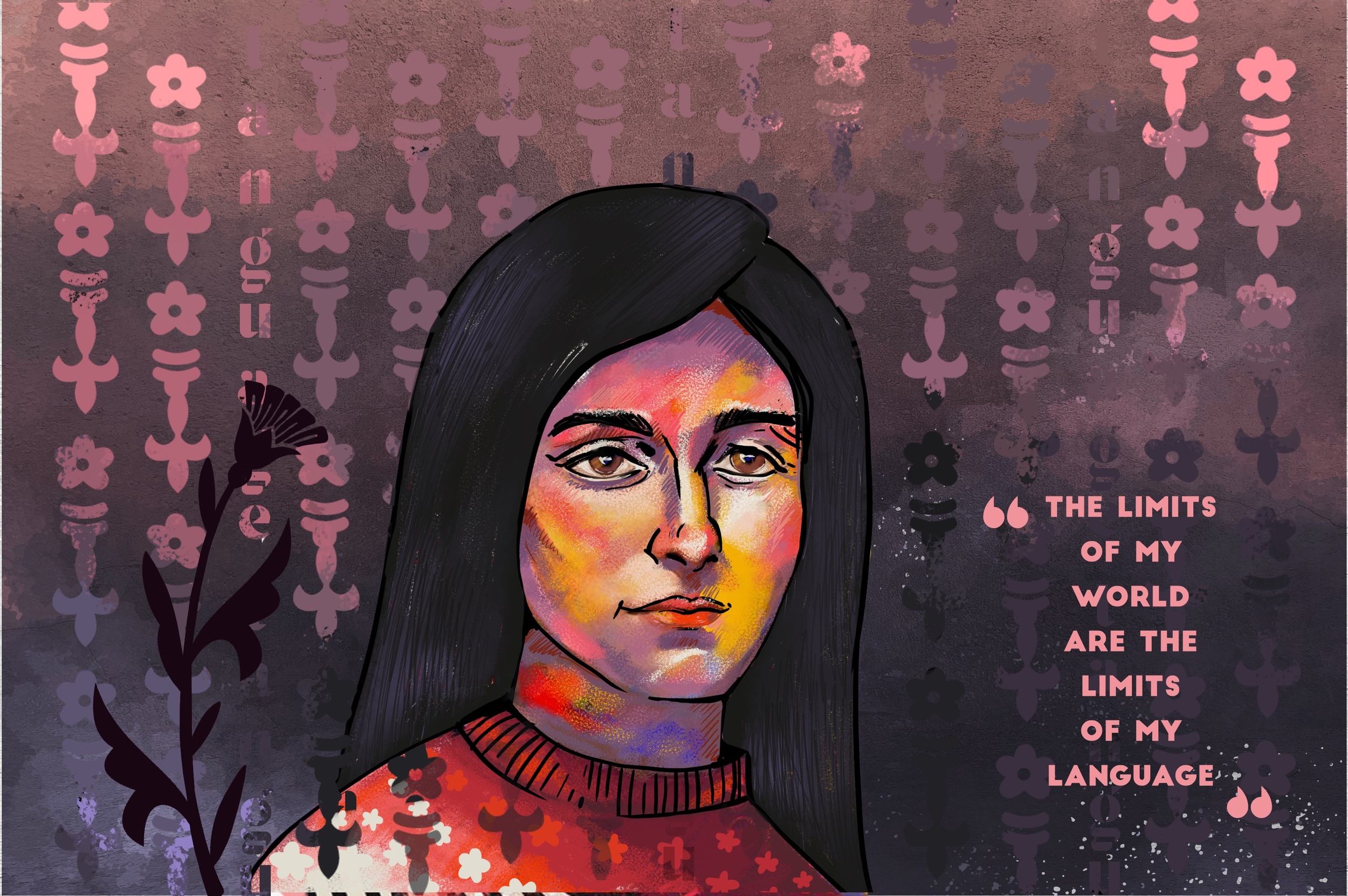


Comments