যখন কোন মানুষ দ্বিতীয় একটি ভাষা শিখে তখন তার মধ্যে এক অন্য রকম আবেগ এবং উৎফুল্লতা কাজ করে। একটি ভাষার শব্দ ও বাক্যাংশের সাথে অন্য ভাষার শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থের মধ্যে কখনো এক-একটি করে মিল পাওয়া যায় না। এমনকি সবচেয়ে সাধারণ অভিব্যক্তিগুলোরও সামান্য ভিন্ন অর্থ থাকে, যা প্রতিটি ভাষার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা থেকে উদ্ভূত। ভাষা পরিবর্তন করার সময়, আমরা অনুভব করতে পারি যেন এক জগৎ থেকে আরেক জগতে প্রবেশ করছি। প্রতিটি ভাষা আমাদেরকে বিশেষভাবে কথা বলতে ও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো দেখতে বাধ্য করে। কিন্তু এটা কি কেবল একটি ভ্রম? প্রতিটি ভাষা কি সত্যিই আলাদা এক বিশ্বদৃষ্টি ধারণ করে, নাকি তার বক্তাদের চিন্তার নির্দিষ্ট ধরণ নির্ধারণ করে দেয়?
আধুনিক একাডেমিক প্রেক্ষাপটে, এমন প্রশ্নগুলো সাধারণত "ভাষাগত আপেক্ষিকতা" বা "স্যাপির অনুমান" এর আলোচনার মধ্যে পড়ে। সমকালীন গবেষণা এই প্রশ্নগুলোকে নির্দিষ্ট করে সাজাতে মনোযোগী, যাতে সেগুলোকে প্রমাণযোগ্যভাবে পরীক্ষিত করা যায়। কিন্তু ভাষা, মন এবং বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান ধারণাগুলোর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা বিভিন্ন বৌদ্ধিক যুগ অতিক্রম করেছে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাবনা ছিল। এই ইতিহাসের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ভাষাগত আপেক্ষিকতা নিয়ে একধরনের সন্দেহবাদ, যা কেবল তার সংজ্ঞা নির্ধারণের কঠিনতার কারণে নয়, বরং এর অন্তর্নিহিত অনুমান ও পরিণতি নিয়ে গভীর দ্বিধা থেকেও জন্ম নিয়েছে।
ভাষাগত আপেক্ষিকতার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে তা সরাসরি আমাদের মানব ভাষার প্রকৃতি বোঝার ওপর প্রভাব ফেলে। পাশ্চাত্য দর্শনের একটি দীর্ঘস্থায়ী অনুমান, যা অ্যারিস্টটলের কাজে ধ্রুপদীভাবে গঠিত, বলে যে শব্দগুলো কেবল লেবেল, যা আমরা বিদ্যমান ধারণাগুলোর ওপর আরোপ করি অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু ভাষাগত আপেক্ষিকতা ভাষাকে আমাদের চিন্তাভাবনা গঠনে সক্রিয় শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। তাছাড়া, যদি আমরা ভাষাগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এবং তাদের জড়িয়ে থাকা বিশ্বদৃষ্টিকে অনুমোদন করি, তবে আমাদেরকে মানবজাতির সাধারণতার প্রকৃতি সম্পর্কিত কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এমনকি কি হতে পারে, ভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর চিন্তা ও উপলব্ধির মধ্যে অতিক্রম করা অসম্ভব ফাঁক বিদ্যমান?
আমাদের বর্তমান ভাষাগত আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত ধারণার শেকড় অন্তত ১৭শ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৮শ শতাব্দীর আলোকায়ন যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। আলোকায়ন কালের আলোচনাগুলোতে প্রায়ই "ভাষার প্রতিভা" বা le génie de la langue (ফরাসি শব্দ) দিয়ে ব্যাখ্যা করা হতো। এই শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হতো, এমন পর্যায়ে যে, এর সঠিক মানে প্রায়ই অস্পষ্ট থেকে যেত। এক সমসাময়িক ভাষ্যকার বলেছিলেন: “আমরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, একটি ভাষার প্রতিভা কী, এবং এটি বলা কঠিন।” তবে আমরা বলতে পারি, একটি ভাষার প্রতিভাকে বোঝা হতো তার স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে, সেই je ne sais quoi যা প্রতিটি ভাষাকে নিজস্বভাবে অনন্য করে তোলে। প্রায়ই ধারণা করা হতো, এই স্বতন্ত্র চরিত্রটি সেই ভাষাভাষীদের জাতীয় মানসিকতার প্রতিফলন।
একটি ধ্রুপদী এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী রূপায়ণ আসে ১৭৭২ সালে জার্মান দার্শনিক ও কবি জোহান গটফ্রিড ভন হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩)-এর Treatise on the Origin of Languageগ্রন্থে। সমসাময়িকদের বিপরীতে, যারা মানব ভাষার চূড়ান্ত উৎসকে প্রাণীর ডাকের সাথে তুলনা করেছিলেন, হার্ডার জোর দিয়েছিলেন যে প্রাণী ও মানব যোগাযোগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। হার্ডারের মতে, মানব ভাষা নির্ভর করে মানুষের এক অপরিহার্য ক্ষমতার ওপর আর তা হল "পর্যবেক্ষণ" (Besonnenheit), অর্থাৎ আমাদের নিজেদের চিন্তাকে চেনা এবং আমাদের সাথে সম্পর্কিত সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা। আমরা যখন শব্দ তৈরি করি, তখন আমরা নাম দেওয়া বস্তুর গুণাবলির ওপর প্রতিফলন করি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটিকে বেছে নিই। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেয়, যার ফলে প্রতিটি ভাষা তার নিজস্ব রূপে বিশ্বের সামান্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভাষাগুলো সংরক্ষিত হতে হতে এসব পার্থক্য জমা হতে থাকে, ফলে ভাষাগুলো এবং তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বদৃষ্টিগুলো ক্রমেই ভিন্নতর হয়ে ওঠে। প্রতিটি ভাষার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে, আমাদেরকে শব্দের রূপগুলো তাদের ব্যুৎপত্তিগত উৎস পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে।
হার্ডারীয় ধারা ১৯শ শতাব্দীর শুরুতে গ্রহণ করা হয় এবং উইলহেল্ম ভন হামবোল্ট (১৭৬৭-১৮৩৫) ভাষা ও সাহিত্যের এক বিস্তৃত আলোচনায় এটিকে দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেন। হামবোল্ট ভাষাগত নিয়তিবাদের একটি উপাদানকে সমর্থন করেছিলেন অর্থাৎ, ভাষা কেবল একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিকে প্রতিফলিতই করে না বরং সক্রিয়ভাবে তা গঠনেও জড়িত: তিনি লিখেছিলেন, "ভাষা হলো চিন্তার গঠনতন্ত্র"। তবে তিনি যে সম্পর্ক কল্পনা করেছিলেন, তা একমুখী ছিল না বরং দ্বন্দ্বাত্মক। ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এক অন্তহীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিদ্যমান: আমাদের চিন্তা আমাদের শব্দকে গড়ে তোলে, আর আমাদের শব্দ আমাদের চিন্তাকে। তার আলোচনায় কেবল পৃথক শব্দ নয়, বরং বিশ্বের ভাষাগুলোর ব্যাকরণিক কাঠামো আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু হামবোল্টের মতে, ব্যাকরণের অধ্যয়নও ছিল আসল কাজের জন্য একটি প্রাথমিক ধাপ মাত্র। ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার একটি ভাষার "মৃত কঙ্কাল" মাত্র। ভাষার চরিত্রকে ধরতে হলে, তার "জীবন্ত কাঠামো" দেখতে হলে, আমাদের অবশ্যই তার সাহিত্যকে মূল্যায়ন করতে হবে, সেই ভাষাটি যেভাবে তার সর্বাধিক বাকপটু বক্তা ও লেখকেরা ব্যবহার করেছেন।
স্টেইনথাল বিশ্বাস করতেন, একটি ভাষার অভ্যন্তরীণ রূপ জাতীয় মানসিকতার সেরা জানালা।
হামবোল্ট ভাষার জীবন খুঁজে পেতে সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিতে বললেও, ১৯শ শতাব্দীর তার উত্তরসূরিরা ভাষার শ্রেণিবিন্যাস করতে মনোনিবেশ করেছিলেন, যা আবর্তিত হতো তাদের ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঘিরে। লক্ষ্যকে প্রায়শই বলা হতো প্রতিটি ভাষার "অভ্যন্তরীণ রূপ" শনাক্ত করা। "অভ্যন্তরীণ রূপ" ছিল হামবোল্টের ব্যবহৃত (যদিও অল্প সময়ের জন্য) একটি শব্দ, যা ভাষার অন্তর্নিহিত গঠন ও সংগঠনকে বোঝাতো, এর "বহিরঙ্গ রূপ"-এর বিপরীতে, যেখানে শব্দ, ব্যাকরণ ও ধ্বনি ব্যবস্থার বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত। হামবোল্টের "অভ্যন্তরীণ রূপ" আলোকায়ন যুগের "ভাষার প্রতিভা"-র ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আর "বহিরঙ্গ রূপ" অন্তর্ভুক্ত করে নামের বিভক্তি, ক্রিয়ার রূপ, নিয়মিত ধ্বনি পরিবর্তন ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়।
হামবোল্টের ধারায় কাজ করা অনেক পণ্ডিত তার "অভ্যন্তরীণ রূপ" গ্রহণ করেছিলেন এবং তা ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারিত করেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপটি বর্ণনা করেছিলেন হেইমান স্টেইনথাল (১৮২৩-১৮৯৯)। "অভ্যন্তরীণ রূপ" স্টেইনথালের ভাষা শ্রেণিবিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, যা আবার তার Völkerpsychologie (জাতিসমূহের মনোবিজ্ঞান বা নৃতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান)-এর হৃদয়ে ছিল। Völkerpsychologie-এর সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল প্রতিটি জাতির অনুমিত যৌথ মানসিকতাকে বর্ণনা করা। একটি ভাষার অভ্যন্তরীণ রূপ, স্টেইনথালের বিশ্বাস অনুযায়ী, জাতীয় মানসিকতার সেরা জানালা ছিল।
কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর মধ্যে, জাতীয় মানসিকতা এবং ভাষার চরিত্র নিয়ে আলোচনা একাডেমিক ভাষাতত্ত্ব থেকে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। এ সময় তুলনামূলক ঐতিহাসিক ব্যাকরণ ভাষাতত্ত্বের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতি সতর্কভাবে শব্দ ও ব্যাকরণিক রূপগুলো তুলনা করে তাদের ঐতিহাসিক পরিবর্তন শনাক্ত করতে এবং সম্ভাব্য বংশানুক্রমিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব আমাদের বলে যে, ফরাসি, ইতালীয় ও স্প্যানিশ সবই ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত; হিন্দি-উর্দু, বাংলা ও পাঞ্জাবি সংস্কৃতের উত্তরসূরি; এবং এগুলোসহ ইউরোপের পশ্চিম থেকে ভারতের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত প্রচলিত বহু ভাষা বিস্তৃত ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত।
এই বৃহৎ পরিবারের কাল্পনিক পূর্বপুরুষ প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় হারিয়ে গেছে, কিন্তু এর শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ ও ধ্বনি ব্যবস্থার উপাদানগুলো এর উত্তরসূরিদের বৈশিষ্ট্য থেকে পুনর্গঠন করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এগুলো সবই ভাষার "বহিরঙ্গ রূপ"-এর দিক – এবং যারা এগুলো অনুসন্ধান করেছিলেন তারা "ধ্বনিগত আইন"-এর শর্তে এসব পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করতেন। ধ্বনিগত আইন কেবল তথ্যগত বিবৃতি, যেখানে বলা হয় যে মূল ভাষার একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি পরবর্তী ভাষাগুলোতে কোন ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা কোনো গোপন, অন্তর্নিহিত নীতির উল্লেখ এড়িয়ে চলে। অধিকাংশ তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাকরণবিদ বিশ্বাস করতেন, ভাষাতত্ত্বকে একটি গুরুতর বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করতে হলে তাকে অবশ্যই দৃঢ়, বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ভাষার অন্তর্জীবন উন্মোচন, তাদের চরিত্র ও চিন্তা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক ধরার প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান গড়ে ওঠার ভবিষ্যৎ কাজ হিসেবে দেখা হতো; আর ন্যূনতম ক্ষেত্রে এটিকে কেবল অলস অধিবিদ্যাগত কল্পনা মনে করা হতো।
১৯শ শতাব্দীর একাডেমিক ভাষাতত্ত্বে হামবোল্টীয় ঐতিহ্যের শেষ প্রচেষ্টায়, সিনোলজিস্ট ও ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ ভন ডের গাবেলেনৎস (১৮৪০-১৮৯৩) "টাইপোলজি" নামক একটি নতুন উপক্ষেত্র প্রস্তাব করেছিলেন, যা বিশ্বের ভাষাগুলোর ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে আবিষ্কার করা যায় "প্রধান বৈশিষ্ট্য, শাসক প্রবণতা" যা ভাষাগত কাঠামো নির্ধারণ করে। এই প্রচেষ্টা ভাষাতত্ত্বের "সর্বোচ্চ কাজ"-এর জন্য একটি প্রমাণভিত্তি সরবরাহ করত, অর্থাৎ এসব কাঠামোগত প্রবণতাকে জাতীয় মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা। তবে গাবেলেনৎসের এই আহ্বান গুরুত্ব পায়নি, কারণ এই যুগে ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ব্যাকরণই ছিল প্রধান। টাইপোলজি কেবল ২০শ শতাব্দীর শুরুতে ভাষাতত্ত্বে মূলধারার অনুসন্ধান হিসেবে পুনরায় আবির্ভূত হয়।
একই সময়ে, আটলান্টিকের অপর প্রান্তে, মানস ও ভাষার প্রশ্নগুলো হামবোল্টীয় প্রভাবিত নৃতত্ত্বে প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছিল। আমেরিকান নৃতত্ত্বের জনক ফ্রান্জ বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২) উত্তর আমেরিকার আদিবাসী ভাষাগুলোর একটি নির্ভুল সংকলন তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করেন, যা বহুখণ্ডে প্রকাশিত Handbook of American Indian Languages-এর মাধ্যমে শুরু হয় (প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে)। বোয়াসের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ব্যাকরণিক বিবরণীগুলো "প্রতিটি ভাষার অভ্যন্তরীণ রূপের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল" হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। "অন্যভাবে বললে," বোয়াস ব্যাখ্যা করেছিলেন, "ব্যাকরণ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন একজন বুদ্ধিমান ভারতীয় তার নিজের চিন্তাধারাকে নিজের ভাষার রূপ বিশ্লেষণ করে বিকশিত করতে যাচ্ছে।"
চলবে........................
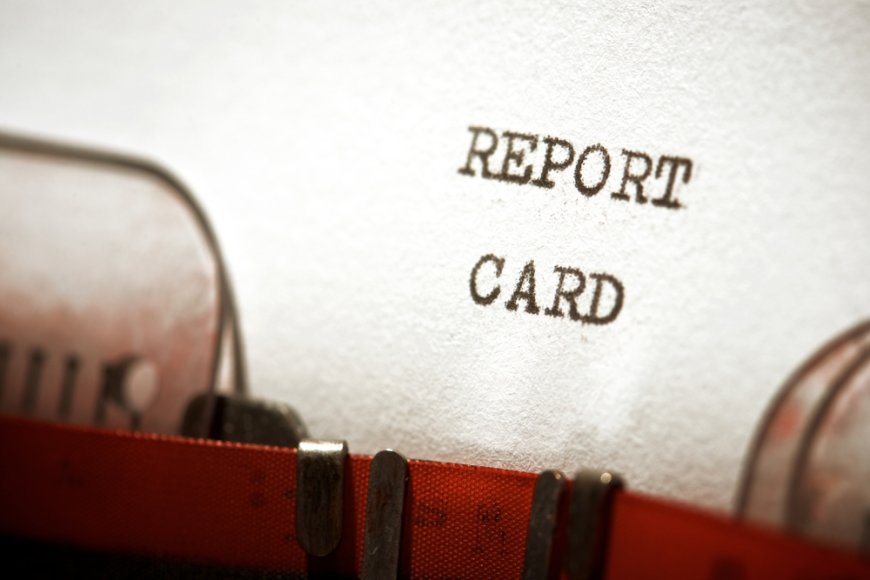


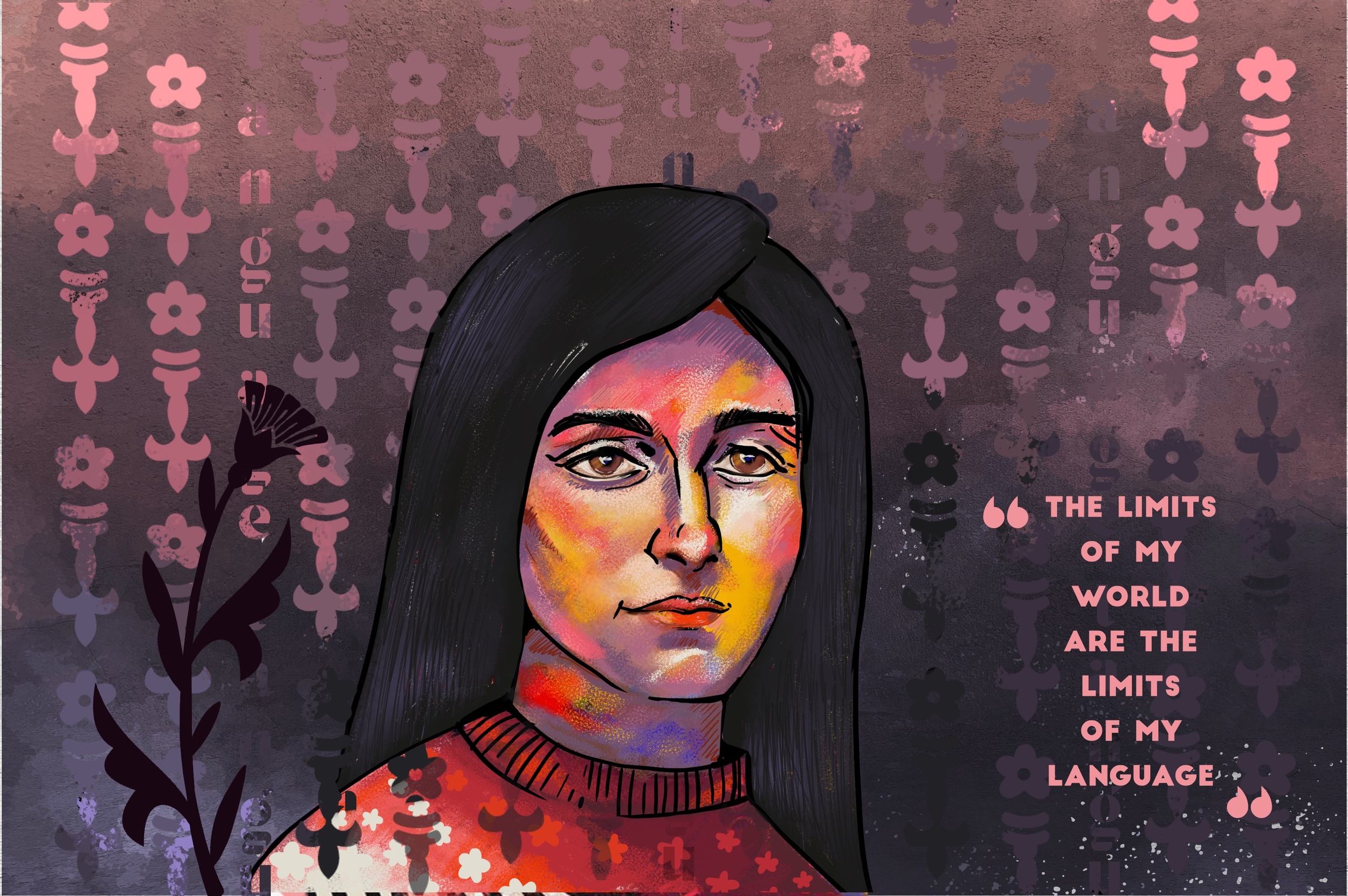



Comments